নুজহাত ইসলাম নৌশিন
আর্থরাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর দশজন সাহিত্য-সমালোচক যেখানে সাহিত্যে নজরুলকে নিয়ে একধরনের চিন্তা-ভাবনা করেছেন, সেখানে নজরুলকে নান্দনিকতার মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত নজরুলসাহিত্য-গবেষক মাওলা প্রিন্স তাঁর অনু্ধ্যানে নজরুল গ্রন্থে। এই বইটি আমাকে নজরুল সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে সাহায্য করেছে। গড়পড়তা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনাকে খুব একটা আমলে না এনে নজরুলের সৃষ্টিকর্ম এখানে গুরুত্ব পেয়েছে নান্দনিকভাবে। রূপতাত্ত্বিক, পুরাণতাত্ত্বিক, সংখ্যাতাত্ত্বিক, জারিপিক কিংবা তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে নজরুল এ গ্রন্থে মূল্যায়িত হয়েছেন।
দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্বে, বিশ্লেষণের গভীরত্বে আর গদ্যশৈলীর চমৎকারিত্বে মন ও মগজকে সজোরে নাড়া দেয়া প্রবন্ধের সংকলন অনুধ্যানে নজরুল। শতবর্ষ পরে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে নজরুলকে নবোদ্যমে আবিষ্কারের ঐকান্তিক মগ্নতা এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রেমে, জ্ঞানে, সৌন্দর্যে, ধ্যানে এবং তারুণ্যের প্রতিশ্রুত অনুশীলনে। এই গ্রন্থে নজরুলের ‘কবিতা ও গান’, ‘ছোটগল্প ও উপন্যাস’, এবং ‘অভিভাষণ ও চিঠি’ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম ‘নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ : প্রসঙ্গ পুরাণ ও পৌরাণিক কাব্যব্যাখ্যা’। যেখানে পুরাণ-বিবরণোত্তর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার পৌরাণিক কাব্যরূপ রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘শিল্পীর উত্তরণ : প্রসঙ্গ দোলন-চাঁপা ও সিন্ধু-হিন্দোল’-এ শিল্পী হিসেবে নজরুলের ক্রম-উত্তরণের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধ ‘বুলবুল : কাব্যসত্যের রূপ-রূপায়ণ’। এখানে শাশ্বত প্রেমের অমর বাণী বুলবুল শুধুমাত্র সাঙ্গীতিক নয়, সাহিত্যিক মূল্যায়নেও যে উৎকৃষ্টতার রাজমুকুট পরিধান করতে পেরেছে, তা রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ প্রবন্ধ ‘নজরুলের দীর্ঘকবিতা : বিষয় ও প্রকরণ’-এ ‘দ্রোহ ও জাগরণ : চির উন্নত মম শির!’, ‘প্রেম ও প্রকৃতি : তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।’, এবং ‘স্তুতি ও মানবতা : মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী!’ উপশিরোনামে উঠে এসেছে একজন ‘সামূহিক মানুষ’ নজরুলের সামগ্রিক কবিসত্তার অনিন্দ্যসুন্দর পরিচয়-স্বরূপ। পঞ্চম প্রবন্ধ ‘নজরুল-কাব্যে পুরাণ : প্রবাহমালা ও পরিসংখ্যান’। এখানে নজরুলের কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের স্বরূপ নির্ণয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে ‘বাঁকবদল ও প্রবাহমালা’ এবং ‘পৌরাণিক বিষয়াদি ও পরিসংখ্যান’ উপশিরোনামে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিন্যস্ত হয়েছে রাজনৈতিক নান্দনিকতার প্রধানতম কবি-পুরোধা কাজী নজরুল ইসলামের পুরাণচেতনার বিবর্তন, উপকরণ ও কারণসমূহ। ষষ্ঠ প্রবন্ধ ‘নজরুল সঙ্গীতে ফিউশন : প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন’। সমাজবিজ্ঞানের সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি ও সমালোচনা-সাহিত্যতত্ত্বের যুগল মিশ্রণে গড়ে ওঠা এ-প্রবন্ধে নজরুল-সঙ্গীতে ফিউশনের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। এ-পর্বে ফিউশন সংক্রান্ত অনাসৃষ্টি ও উদ্বেগজনিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে তিন স্তরের সুপারিশমালা হয়েছে সংযোজিত।
পরবর্তী অধ্যায় ‘ছোটগল্প ও উপন্যাস’। এখানে ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের সুদৃঢ় অবস্থান বিশ্লেষিত হয়েছে সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রবন্ধে। সপ্তম প্রবন্ধ ‘নজরুলের ছোটগল্প : বিষয় ও বিন্যাস’-এ ‘প্রেম ও প্রকৃতি’, ‘সমাজ ও সংস্কার’ এবং ‘জননী ও জন্মভূমি’ তিনটি উপশিরোনামে নজরুলের তিনটি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে; যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে গল্পের শৈলীগত সৌন্দর্যবিচার। অষ্টম প্রবন্ধ ‘মৃত্যু-ক্ষুধা ও পদ্মানদীর মাঝি : ঐতিহ্য-পরম্পরা’। এতে তুলনামূলক পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়েছে অগ্রজ-ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলামের ঔজ্জ্বল্য। নবম প্রবন্ধ ‘বাংলা উপন্যাসে নজরুলের প্রভাব : একটি অনুসন্ধানী পাঠ’। এখানে নজরুলের উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যিক দিকগুলো বিবেচনায় রেখে বাংলা ও বাংলাদেশের উপন্যাসে তাঁর প্রভাবক্ষম প্রতিভাকে তুলে ধরা হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায় ‘অভিভাষণ ও চিঠি’-র ‘নজরুলের অভিভাষণ : অন্তরঙ্গ অবলোকন’ এবং ‘নজরুলের চিঠি : ইচ্ছার দলিল’ প্রবন্ধ দুটিতে পোশাকি আস্তরণের অন্তরালে ব্যক্তি-নজরুলের পরিচয় অনুসন্ধান করা হয়েছে। তিনটি অধ্যায়ের পর সবশেষ ‘পরিশিষ্ট’ অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে ‘শ্রেণিবদ্ধ নজরুল সাহিত্যকর্ম ও সারসংক্ষেপ’ প্রবন্ধ। এখানে নজরুলের সকল গ্রন্থের পরিচিতি ও সারকথা যুক্ত হয়েছে অভিনব কৌশলে।
অনুধ্যানে নজরুল গ্রন্থটিতে সর্বতোমুখেী-প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে নন্দনতত্ত্বের বিচারে। বইটির ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল; যা পাঠককে শেষ অবধি টেনে ধরে রাখে। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ওপর লেখা মাওলা প্রিন্সের অনুধ্যানে নজরুল একটি অনবদ্য গ্রন্থ; এ গ্রন্থ যে কালজয়ী হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।


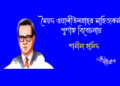








Discussion about this post