আকলিমা আঁখি
জন্ম, মৃত্যু, দিনযাপন¾ মোটাদাগে জীবনচক্র যেন এরমধ্যেই আবর্তিত। জন্মের চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। আর, আমৃত্যু সুন্দরভাবে বাঁচার যে সাধনা, সেই সাধনা যেন যুদ্ধেরই নামান্তর। বলা যেতে পারে, আমৃত্যু সুন্দরভাবে বাঁচার সে সাধনা হলো অনন্ত জীবনতৃষ্ণা ও নিরন্তর বাঁচার লড়াই। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার সংগ্রামটাই জীবন, জীবনের সৌন্দর্য, জীবনের পূর্ণতা। এজন্যই বাঁচার জন্য মানুষের এতো আকুলতা, এতো তীব্র জীবনাকাক্ষা :
বস্তুত, কোনো মানুষই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার জন্য কোনো মানুষ কখনো প্রস্তুত থাকেও না। শত কিংবা হাজার অথবা লক্ষ দুঃখ-কষ্ট-হতাশার মধ্যে থেকেও কোনো মানুষ সুস্থ জ্ঞানে অনিশ্চিত স্বর্গ-নরকে যেতে চায় না। এজন্যই তো এতো কান্না, এতো অশ্রুপাত। (মাওলা প্রিন্স, বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি, ২০২২ : ৪৯-৫০)
মানুষের জীবনের এই চরম সত্যের শব্দগাঁথাই মাওলা প্রিন্স (জন্ম : ১৯৮৩)-এ বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি (২০২২) উপন্যাস।ঔপন্যাসিকের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস এটি; কিন্তু, প্রথম উপন্যাস হিসেবে এই উপন্যাসটি অনভিজ্ঞ তরুণ কথাসাহিত্যিকের উচ্ছ্বসিত আবেগের স্ফুরণমাত্র নয়। উপন্যাসটিতে একজন নিবিড় পর্যবেক্ষণশীল অনুসন্ধানী পরিশ্রমী গবেষক, প্রাবন্ধিক, সত্যিকারের জ্ঞানসাধক, জীবনাভিজ্ঞ দার্শনিক এবং সেইসাথে মিশেছে তাঁর সহজাত কবিত্ব। মানুষের জীবনকে তিনি বিচিত্র বিভঙ্গে আবিষ্কার করেছেন। জগত-জীবন, মানুষ-প্রকৃতি, পরিবার-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি, তথ্য-তত্ত্ব, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সংস্কার-সংস্কৃতি, শিক্ষা-মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথ-নৃতত্ত্ব, দেশকাল, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমসাময়িক ঘটনা সর্বাত্মক অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার সারবত্তাকে নিঙড়ে দিয়েছেন উপন্যাসটিতে। জীবন ও সৃষ্টির প্রতি সততই সচেতন এবং দায়বদ্ধ মাওলা প্রিন্সের গ্রন্থসমূহ হলো : কাব্যগ্রন্থ¾ স্বতঃস্ফূর্ত-কথা : নিশীথপ্রদীপে শঙ্খঝিনুকের চাষ (২০১৩), দিবারাত্রি প্রেমকাব্য (২০১৪), সব ঠিক, ঠিক কি, ঠিকটা কী (২০১৯), আবার কুড়ি বছর পর (২০২০), এক কথা একশো বার (২০২৪)। উপন্যাস¾ জমানো-কথা : বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি (২০২২)। গবেষণা¾ বিধিবদ্ধকথা : কালোত্তরের প্রতিশ্রুতি : প্রসঙ্গ সাহিত্য (২০০৯), রশীদ করীমের উপন্যাস : বিষয়বৈভব ও শিল্পরূপ (২০১৪), অনুধ্যানে নজরুল (২০১৭), কথাসাহিত্যপাঠ ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (২০০৯), নজরুল পৌরাণিক অভিধান (২০২০), নজরুল ও জীবনানন্দের কবিতায় পুরাণ ও চিত্রকল্প (২০২২), ভাষা–আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য (২০২৪), বাংলাদেশের সাহিত্য : উৎস ও উত্তরণ (প্রকাশিতব্য), রংপুর বিভাগের আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ (প্রকাশিতব্য) ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ (প্রকাশিতব্য) ইত্যাদি।
বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে মূল দুটি স্রোতে নির্দেশ করা যায়। যথা : এক. বিশ্বব্যাপী করোনার প্রভাব ও করোনাকালীন জীবনবাস্তবতা-সমস্যা-সংকট। এবং দুই. ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণ সূত্রে আভাসিত গ্রামকেন্দ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার চিত্র। এই দুই ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের দুই প্রজন্মের দুই সময়কালকে বিশ্লেষণ করে এমন এক বস্তুবিশ্ব নির্মাণ করেছেন যেখানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনের সমগ্রতা সৃষ্টির প্রয়োজনে অতীত ও বর্তমান এবং নগর ও গ্রামীণ জীবনপ্রবাহকে অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করেছেন। সত্যিকার অর্থে, “সাহিত্য, শিল্প, জীবন, ব্যক্তি, সমাজ¾ এই অঙ্গগুলো আলাদাভাবে থাকে না। লেখকের চিন্তার সামগ্রিকতার মধ্যেই এর অবস্থান।” (ড. স্বপ্না রায়, বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা, ২০০৬ : ১৩) উপন্যাসের প্লট সমসাময়িক জীবনভিত্তিক, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিনির্ভর যে প্লট তৈরি করেছে মূলত সময়। চরম অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকা অবরুদ্ধ সময় লেখককে তাড়িত করেছে, আলোড়ন তুলেছে চৈতন্যে। উপন্যাসে বর্ণিত ভয় ও সাহস, স্বস্তি ও যন্ত্রণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ-বেদনার ঘূর্ণিপাকে চক্রাকারে ঘুরেছেন, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, একফোঁটা প্রশান্তির খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটেছেন একসময় থেকে অন্যসময়ে। এভাবে করোনাকালীন জীবনবাস্তবতা উপন্যাসের বস্তুবিশ্বকে নির্মাণ করেছে। একটা স্থবির, নিশ্চল, অবরুদ্ধ সময়, থমকে যাওয়া জীবন ও জীবিকা, অক্সিজেন ও মাস্কে আটকেপড়া রুদ্ধশ্বাস জীবন, বিষাদগ্রস্ততা, আতঙ্ক, মৃত্যুভয়, আশঙ্কা, উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা স্বাভাবিক জীবনস্রোতে এক বিরাট পরিবর্তন নিশ্চয়ই; কিন্তু, করোনাকালীন স্থবিরতার বিপরীতে করোনা-পূর্ববর্তী অস্থির সময়কেও লেখক তুলে ধরেছেন :
কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস আসবার আগে গোটা পৃথিবীর সবাক চিত্রটা একটু মনে করোতো দেখি; মানুষের বাড়-বৃদ্ধি কী কম হয়েছিলো, কে কাকে ধরবে, কে কাকে মারবে, কে কাকে অপদস্থ করবে, কে কাকে জেলহাজতে ঢুকাবে, কে কার প্রমোশন-আপগ্রেডেশন আটকাবে, কে কার চাকুরী খাবে, কে কার চরিত্র হরণ করবে, কে কতো বেশি মুনাফা হাতাবে, সরকারি কাগজে একটা বালিশ কিংবা একটা পর্দা কিংবা একটি গাছের দাম কতো টাকা দেখাবে, একটা প্রজেক্টে কতো কামাবে, কে কটা ফ্ল্যাট কিনবে, কে কতো জায়গা জমি নামে-বেনামে রাখবে, কার হাতে কিংবা হাতে-পায়ে কতো পাওয়ার; শুধু কী তাই, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তা আর জঙ্গিবাদের আওয়াজ তুলে সবকিছুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি, আজ এ দেশকে শাসাচ্ছে, কাল ও দেশকে নজরদারিতে রাখছে, পরশু আর এক দেশকে আক্রমণ করছে, তারপরদিন অন্যকোনো দেশের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করছ; […] রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু কিংবা চুরি-ডাকাতি কোথায় ছিলো না? দেশের ভেতরে কিংবা বাহিরে পুরো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছিলো বা চলছিলো শুধু মানবতার কান্না, মনুষ্যত্বের আর্তনাদ আর ষড়যন্ত্রের পূজা-অর্চনা। (২০২২ : ৫১)
২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বের সামনে যে নতুন মহাসংকট, সে এক মহাযুদ্ধ। যাকে অনেকে ‘নব্য ঠাণ্ডা যুদ্ধ’ নাম দিয়েছেন। ঔপন্যাসিকও করোনাকে ‘যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ এমন এক অদৃশ্য শক্তি, যার গতি-প্রকৃতি সহজেই বুঝে নেয়া যায় না। বরং এই করোনা মহামারী বিচলিত করে তুলেছে পুরো বিশ্বকেই। শুধু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোই নয়, বরং সাজানো-গোছানো, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের শীর্ষে থাকা উন্নত দেশগুলোও কীভাবে নাকানিচুবানি খেয়েছে¾ তারই দৃশ্যপট উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক :
দিন পেরুলে দুই-তিন-চার হাজার করে জ্যান্ত মানুষ শামিল হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসহায় এক মৃত্যর মহামিছিলে। সময়টা অদ্ভুত। এমনটা কেউ কখনো দেখেনি। পৃথিবীর সবদেশ সবমানুষ এক নিয়মে ঘরবন্দি, এক ভাবনায় আচ্ছন্ন, এক শঙ্কায় শঙ্কিত, এক আতঙ্কে আতঙ্কিত, এক গবেষণায় নির্ঘুম।[…] জীবন এখন সীমিত। জীবিকা এখন শিকেয় তুলে রাখা সংরক্ষিত বাতাসা-সন্দেশ। (২০২২ : ০৮)
করোনার অভিঘাত এসে লাগে বাংলাদেশেও, ৮মার্চ ২০২০ প্রথম শনাক্ত, ১৮মার্চ ২০২০ প্রথম মৃত্যু। এভাবে একে একে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে মহামারী-অতিমারীর মতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ এবং এর প্রভাবে বিপর্যস্ত জনজীবন, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন, শ্রমিক ছাটাই, আতঙ্ক, উত্তেজনা, বিভ্রান্তি, বিকল রাষ্ট্র-প্রশাসন, শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে না পারা রেস্টুরেন্ট মালিকরা, গার্মেন্টস মালিকদের সিদ্ধান্তহীনতা¾ গার্মেন্টসগুলো কখনো কর্মীদের ফোন করে ডাকছে, আবার মিডিয়ার সামনে বলছে, সবার আসার প্রয়োজন নেই, আন্তর্জাতিক বাজার হারানোর আশঙ্কায় মালিক শ্রেণির তালবাহানা, অন্যদিকে দিশেহারা নিম্ন-আয়ের শ্রমিকেরা। ‘কাজের আশায়, পাওনা বেতনের দাবিতে, বেঁচে থাকার যুদ্ধে, জীবনের সন্ধানে’ দলবেঁধে পায়ে হেটে পাড়ি দেয় শত শত কিলোমিটার :
করোনা হামাক কিছু কইরবে না, করোনা আমাগো কিছু কইরব্যার পাইতো না, হামরা কিংবা আমগো না খায়্যায় মরমো, মইর্যা যাইবো, কাইজ না কইরলে টেহা-টেকা-টাকা দ্যায় নিহি! (২০২২ : ১৭)
রাস্তায় বাড়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনির কঠোর নজরদারী। তবুও নিরূপায় ‘সতর্ক শ্রমিকেরা মাছের ড্রামের ভেতর গুটিসুটি হয়ে বসে ট্রাকে উঠে ঢাকা যায়, নারায়ণগঞ্জ যায়, গাজীপুরে যায়! মিডিয়া এই নিদারুণ চিত্রও ফাঁস করে দেয়! গরিবের শান্তি নাই, গরিব মানুষ জীবন বাঁচানোর জইন্য মাছের ড্রামে করি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর গেইলে করোনা ছড়ায়, বড়লোকেরা প্রাইভেট গাড়িতে চইড়ে ঈদ কইরতে দ্যাশের বাড়ি গেলি করোনা পালায়, উল্টা পথে দৌড়ায়, লৌড়ায়!’ (২০২২ : ১৭) কোভিড যে নতুন সংকট ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে সেই প্রেক্ষাপটে নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ঔপন্যাসিক প্রাণপণে এই বিশ্বাস রাখতে চেয়েছেন যে প্রকৃতি যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, করোনার অভিঘাতে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, তেমনি করে এই মহাযুদ্ধ-মহাসংকটকালে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটবে :
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাতে যেমন জাতিসংঘ সৃস্টি হয়েছে, তেমনি প্রতম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই করোনাযুদ্ধে সমগ্র মানুষ, সমগ্র সংস্থা, সমগ্র অঞ্চল ও সমগ্র দেশ একজোট হয়ে আরো টেকসই ও উচ্চতম কিছু তৈরি করবে, সৌহার্দ ও সহমর্মিতা নিয়ে তারা সবাই মিলিত হবে; (২০২২ : ৫২)
কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী শ্রেণির মানুষের স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি; বরং এই সংকটকে অস্ত্র করে কী ভাবে নিজেদের আখের গোছাবে সে চিন্তায় মগ্ন থেকেছে। ঔপন্যাসিক যে পরিস্থিতিকে ‘কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস’ বলে অভিহিত করেছেন।
নিরন্ন-দুঃস্থ মানুষের অধিকার হরণ, ভঙ্গুর স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সার্জিক্যাল পিপিই ও মাস্ক-৯৫ কেলেঙ্কারি, রিলিফ ও টিসিবির চাল-তেল চুরি, অক্সিজেনের সিলিন্ডার, মাস্ক, গ্লাভস নিয়ে ব্যবসা, অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অরাজকতা, বহুমুখী সামাজিক দুর্নীতি, সরকারী ত্রাণ প্রচেষ্টায় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ইত্যাদির বিশ্বস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেশ ও বহির্বিশ্বের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকটকে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজে, প্রশাসনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যে দুর্নীতিচিত্র দীর্ঘ সময় ধরে চলছিলো তার স্বরূপ করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত প্রেম ও শিক্ষাভাবনা এবং সংবাদপত্র, সংবাদকর্মী ও মিডিয়ার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে খণ্ডন করেছেন। মহামারী-অতিমারীর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের সূত্র খুঁজেছেন সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে। বর্তমান মহামারীর সম্ভাব্য প্রভাবের জন্য শিক্ষণীয় উদাহারণ বা প্রতিতুলনা খুঁজেছেন অতীতের মহামারী-অতিমারীর আর্কাইভে। অতীত আলোচনার তাৎপর্যের কথা উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২)-এর রিকুইম ফর এ নান (১৯৫১) উপন্যাসে পাওয়া যায় ‘The past is never dead. It’s not even past.’ অতীতেও যুদ্ধবিপর্যয় ছিলো, প্লেগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রভাব বিশ্বজুড়েই পড়েছে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে; কিন্তু, নিরন্তর প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সে-সমস্তকিছুকে জয় করতেও সক্ষম হয়েছে মানুষ। উপন্যাসে বর্ণনা :
১৮১৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মহামারীতে পৃথিবীতে কতো কোটি কোটি মানুষ যে শুধু কলেরায় মারা গেছে, তার হিসাব নেই; অথচ, মৃত্যুঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আজ কলেরা যেনো কোনো বিষয়ই নয়; (২০২২ : ১১০-১১১)
কলেরার মতো একদিন হয়তো দেখা যাবে করোনা কোনো অসুখই নয়; কিন্তু, করোনাকালীন বাস্তবতা আমাদের শিখিয়েছে অনেককিছু। সাধারণ মানুষকে হেরে যেতে হয় বরাবরই। সমস্তটাই হয়ে উঠে রাজনীতির নব নব কৌশল। তাই বিপন্ন বর্তমানের সমস্যা-সংকট-যন্ত্রণা ও ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউনের নিষ্প্রভ দিনগুলোয় উৎকণ্ঠা আর বিষণ্নতার মাঝে’ নিজে হারাবার কিংবা অন্যকে হারানোর আতঙ্ক যখন বিচলিত করে তোলে তখন লেখকের¾
সুনসান বিছানায় শুয়ে পড়লে মনের সাদাকালো বায়োস্কোপে পারিবারিক কবরস্থানের চিত্রায়ণ ঘটে। বড় একটা সানের উপর কামিনীর ছায়া, পাশে একটা পুরাতন নারিকেল গাছ, একটা লাল জবা ফুলগাছ, দু-চার কিংবা পাঁচটা পাতাবাহরের সঙ্গে একটি আমগাছ বেষ্টিত উর্বর দোআঁশ মাটির তলদেশে আছে পূর্বপুরুষদের হাড়। (২০২২ : ০৯)
একে একে হারানো স্বজনদের মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের চেতনায়। কিংবা, কখনো শৈশব-কৈশোরের স্বপ্ন-কল্পনা, বেড়ে ওঠা, পিতা, মাতা, দাদি-দিদি-দিদিমা, পাগলি নানি, শিল্পী ও সাংবাদিক মেধাবী সৎ-মামার জীবনযুদ্ধ, পারিবারিক দারিদ্র্য, সংগ্রাম, কথকের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিজ্ঞা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, স্নেহ-ভালোবাসার স্মৃতিচারণসূত্রে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও জীবন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় রূপ লাভ করে। উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে ওই অঞ্চলের আর্থসামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাবনা, জীবনযাত্রা ও আচরণ; ফুটে উঠেছে তাদের নৃতাত্ত্বিক আবেগ-ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি ও পরিচয়।
উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে নৈকট্যসূত্রে অর্জিত লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি। উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক পরিবেশ ও উপভাষা ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিবিড় সম্পৃক্ততার পরিচয়। গ্রামীণমানুষের জীবনচর্চার ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস-সংষ্কার। ফুটে উঠেছে তাদের সমাজনির্ভর সংস্কৃতির আবহের রূপাভাস। পান খাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন, কলহ-বিবাদ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, সংস্কৃতির নানাবিধ অনুষঙ্গ¾ নবান্ন উৎসব, ঘুড়ি কাটাকাটি উৎসব, যাত্রা, সার্কাস, জাদুখেলা, পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ দেখা, বিভিন্ন মেলা, হাডুডু প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, জুয়া, চান-ফুল-পয়সা খেলা প্রভৃতির বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সমাজ অভিজ্ঞতার সুনিবিড় পরিচয় বিধৃত। অতঃপর সময়-সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্মৃতিচারণ সূত্রে চলে আসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ :
দিদি, দাদি বা দাদিমার কোলে মাথা রেখে অথবা তার আঁচলে মাথা ঢেকে ঘুমোতে ঘুমোতে শুনি, আমাদের পুরান কিংবা নতুন বাড়িতে আগুন দেয়ার কথা, ত্রিমোহনী কিংবা তিস্তা নদী পেরিয়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পালানোর কথা, দিদি বা দাদির ছোট ভাইয়ের সাথে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তরঙ্গ খাতিরের কথা, দিদি বা দাদিদের পুরানবাড়িতে ওদের আপ্যায়নের কথা। যুদ্ধের আগে অকালে স্বামীহারা এক যুবতী-জননী তার নয়নের মণি কিংবা কলিজার টুকরা সদৃশ মাসুম ছেলেমেয়েদের হারাতে বা কোলছাড়া করতে চান নি। কী দিনই না গ্যাছে তখন, এ্যালোড্রাম থাকি মিলিটারি আইস্যার খবর পায়্যা আকার ভাত আকাত থুয়্যা ছয়-ছয়টা মাউরিয়া ছাওয়া নিয়্যা বাড়ির পিছনের আড়াবাড়ির ভেতর দিয়্যা সড়কত উঠি ত্যামনির ঘাট পার হয়্যা খুনিয়াগাছ-কালমাটি বরাবর দৌড়, দৌড়, দৌড়!’ (২০২২ : ৯-১০)
এই নিরন্তর ছুটে চলা, দৌড়ানো, পালানোই যেন জীবনের নিয়তি¾ স্থান থেকে স্থানে, সময় থেকে সময়ে, স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে¾ যুদ্ধ, মহামারী-অতিমারী, বন্যা, আমপান-ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষের আভাস, তিন ফুটের দূরত্ব, মানুষে মানুষে সন্দেহ, এমন আরো অসংখ্য-অগণিত সমস্যা-সংকটের মাঝে। স্তব্ধ নগরীর বিষণ্নতার ভিতর একফোঁটা স্বস্তি কিংবা একটুকরো বিনোদন যেন সপরিবারে লুডুখেলা, ‘ছয়, ছয়… ছক্কা কিংবা এক, এক…।’ অথবা, স্ত্রী-সন্তানের সাথে কাটানো আনন্দ অনুভূতিগুলো, কিংবা সন্তানদের সাথে ধাঁধা, ছড়া আর রসিকতায় মোড়ানো হাহাহা… হিহি… হোহো হেসে উঠা মুহূর্তগুলোই যেন জীবনের অমূল্য সম্পদ :
এই তো জীবন, অবিরল কান্না কিংবা শোকাহত হওয়ার পুনরাবৃত্তি ভেঙে হেসে ওঠাই তো জীবন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউনের নির্বাক নিঃশব্দ মূহূর্তে নিষ্পাপ নিঃশর্ত হাসিই তো জীবনের বার্তা। (২০২২ : ৬৩)
এই ক্ষুদ্র মূহূর্তগুলোই জীবনকে ভিন্নরূপে ভাবতে শেখায় : ‘এই মুহূর্তের আনন্দ ও অনুভূতিগুলো তো মিথ্যে নয়, ঠুনকো নয়, হালকা নয়, ব্যথা ভরা বৃহৎ জীবনে ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়; কোন ধন-সম্পদ, ডলার-পাউন্ড, যশ-খ্যাতি দিয়ে এই নিখাদ ও বিশুদ্ধতম আনন্দ মেলে, পাওয়া যায়, উপভোগ করা সম্ভব!’ (২০২২ : ৮৭)
জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘটে যাচ্ছে একের পর এক ঘটনা¾ ‘হায়, এক জীবনে কতো ঘটনা, কতো গল্প; তারপরও জীবন কতো ছোট!’ (২০২২ : ১১৮) এই ছোট্ট জীবন কত গতিশীল, কত দ্রুত পাল্টে যায় দৃশ্যপট¾ ‘হাঃ জীবন, হায় জীবনের পালাবদল, রূপ ও গতির পরিবর্তন, উত্থান-পতন!’ (২০২২ : ১৩০) জীবনসংগ্রামী দিদি বা দাদি বা দাদিমার মতো এক বিধবা নারীর জীবনযুদ্ধ, সন্তানদের প্রতিপালনে আগ্রহনিষ্ঠা, বৃহৎ পরিবারের ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে নেতৃত্ব দিয়ে এক সুতায় বেঁধে রাখার সক্ষমতা কিংবা পারদর্শিতা কিংবা প্রাণান্ত চেষ্টা, যে নিজে কোনোদিন স্কুলে যায় নি; কিন্তু, সেই গ্রামীণ সাধারণ নারী¾ আধুনিক শিক্ষার প্রতি যার সীমাহীন আগ্রহ, সেই বুদ্ধিমতী ও অহমবোধসম্পন্ন স্বশিক্ষিত নারী দিদিমা যখন শাসনের অজুহাতে নির্দ্বিধায় পুত্রবধূকে ঝাড়ু আর বাড়ুন দিয়ে হরহামেশাই মারধর করেন¾ সেই বিশেষ দৃশ্য ছোট্ট নাতির মনে এমন এক বোধ বা উপলব্ধির জন্ম দেয়, যা ধীরে ধীরে ‘অন্যায়¾ অধর্ম নির্দয়তার ইতিহাস’ তাত্ত্বিক ‘অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যা’র উপলব্ধিতে রূপান্তর হয়।
ঔপন্যাসিক স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে এমন কৌশলে শৈশব ও কৈশোরকে দৃশ্যমান করেন, কেবল বর্ণনা হয়ে থাকে না, পাঠক যেন সহচরি হয়ে লেখকের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যক্ষ করে নিজেই, কিংবা, ঔপন্যাসিকই যেন পাঠককে পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেন :
রাস্তার পাশে জাম গাছের বিপরীতে একটি কাঁঠাল গাছের তলে দেখবে বাঁশের তৈরি একটি প্রশস্ত টং বা বসবার মাচা, তুমিও সেখানে বসতে পারো, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারো, সামনের পুকুরের স্বচ্ছ পানি দেখতে দেখতে মধুর কোনো গল্প করতে পারো গ্রামের দু-চার-পাঁচটা মানুষের সঙ্গে ওখানেই, ওরা তোমাকে সঙ্গ দিবে, ওরা তোমাকে ওদের আনন্দ, বেদনা, হতাশার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ শোনাবে; (২০২২ : ৭৪)
গ্রামীণজীবনের চির চেনা সহজ-সরল-আন্তরিক মানুষের কথা, প্রকৃতির সাথে মানুষের একাত্মতা, মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে ফুল, পাখি, গাছ-গাছালী গভীর প্রশান্তিতে কীভাবে মনকে ভরিয়ে তোলে, কীভাবে মানুষকে আগলে রাখে, তামাক, গম, পাট, ভুট্টা, আলু কিংবা বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, সান বাঁধানো ঘাট, বাঁশঝাড়, কাঁচা ল্যাট্টিন ইত্যাদি নিখুঁতভাবে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি এই অঞ্চলের অভাব-দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়ার কারণ যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পুর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কে, সেইসময়ের বিশেষ করে ষাট থেকে নব্বইয়ের দশকের উত্তরবঙ্গের অভাবের নানামুখী কারণগুলো ঔপন্যাসিক একে একে ব্যাখ্যা করেছেন। অনুর্বর ভূমি, মান্ধাতার আমলের উৎপাদন ব্যবস্থা, ভৌগোলিক কারণে খরাপ্রবণ এলাকা, বিদ্যুতের অপ্রতুলতা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-খরা-পোকালাগা-মড়ক-চরব প্রভৃতি প্রাকৃতিক সংকট, সাবেকী হালচাষ পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষকের সীমাহীন দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত পরিচর্চার অভাব, প্রয়োজনানুযায়ী উপকরণ ক্রয়ে অপারগতা, ফসলতোলা ও ভোগ-সংরক্ষণে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, পণ্যের যথাযথ মূল্য না পাওয়া, বীজের অপ্রতুলতা, মানসম্মত বীজ না থাকা, বীজ সংরক্ষণে সীমাবদ্ধতা, ইঁদুর-বিড়াল-বাদলায় বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
সরকারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগে আঞ্চলিক বঞ্চনা ও বৈষম্য প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক আয়-ব্যয় জরিপ, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার যদিও হ্রাস পেয়েছে কিন্তু উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্য সে অনুপাতে কমে নি এবং এর পেছনে সরকারের পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাব তথা ব্যর্থতাই দায়ী। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার শাসনকালীন রাজনীতি বিশ্লেষণ করে ঔপন্যাসিক আক্ষেপ করে বলেছেন, খালেদা জিয়ার জন্ম-শৈশব-কৈশোর উত্তরবঙ্গে, শেখ হাসিনা রংপুরের পুত্রবধু হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে তাঁদের বিশেষ কোনো নজর ছিলো না, বরং অনীহাই ছিলো। শুধু তাই নয়, এ অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যের তত্ত্বীয় ইতিহাসকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন¾ কীভাবে একজনের উপার্জনের উপর পরিবারের অন্যান্যরা নিশ্চিন্তে নির্ভর করে থাকে, সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন এখানকার জনগোষ্ঠীর স্বভাবগত সহজ, সরল, সৎ, আদর্শিক, আত্মসম্মানবোধ, আবেগপ্রবণতা, বোকা, হাবা, অলস, অনুভূতিহীন, পাষাণ, উদাসীন, বাউদিয়া, কামচোরা, রসিক, মফিজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে।
শুধু নামকরণের সাদৃশ্যের দিকটির জন্য নয়, ঘটনার সাথে সত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সময়ও যে উপন্যাসটির কথা চলে আসে সেটা হল, লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)-এর ওয়ার অ্যান্ড পিস (১৮৬৯)। মিলান কুন্ডেরা (১৯২৯-২০১৩) ‘উপন্যাস, ইতিহাস, ব্যক্তি’ প্রবন্ধে এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধের ৫০ বছর পরে তলস্তয় যুদ্ধের যে ছবি উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন, তা ইউরোপ ও অ-ইউরোপের বাসিন্দাদের জন্য সমান মর্মঘাতী হয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসটি এমনভাবে লেখা যাতে পাঠক ঠিক বুঝতে পারেন না কোনো যুদ্ধ; কিন্তু, তাতে পাঠকের কোনো সমস্যা হয় না। তলস্তয় এখানে মূলত যে বিষয়ে আগ্রহী তা হল, মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক। গোটা উপন্যাসে এটাকেই তিনি অনুসন্ধানের বিষয় করে তুলেছেন। তিনি দেখান, ইতিহাস নিজেই নিজেকে তৈরি করে। কোনো মহান ব্যক্তি বা ঘটনা ইতিহাসকে তৈরি করতে পারে না। এ ঘটনা দেখা যাবে, আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০)-এর বিখ্যাত উপন্যাস দি প্লেগ (১৯৪৭)-এ। উপন্যাসটি মোটেও প্লেগ নিয়ে নয়। ওয়ার অ্যান্ড পিস যেমন শুধু কোনো বিশেষ যুদ্ধ নিয়ে নয়। কাম্যু এখানে স্বৈরাচারী ক্ষমতা ও মহামারীর সময়ে মানুষের স্পিরিট বা এক্সিস্টেনশিয়াল প্রশ্নটাকে খতিয়ে দেখেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিক হল, ঘটনা ও লিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্পিরিট ও সত্যের সম্পর্কের জন্য ঘটনার তথ্যগত সত্যের বাইরেও আছে নিজের সত্তাকে সত্যের সংগ্রামে নিয়োজিত করে সত্যকে বুঝার চেষ্টা। (রেজাউল করিম রনি, ২০২০) যে বিষয়টি আমরা পাই মাওলা প্রিন্সের বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে। উপন্যাসটি কেবল করোনার বিবরণী হয়ে থাকে নি, বরং বিদ্যমান সময়কালের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মানবিক অস্তিত্বের বিপন্নতাকে ধারণ করেছে। বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপনের অভিনবত্বে ঐতিহাসিক উপাদান উন্নীত হয়েছে চিরায়ত সংগ্রামী জীবনাকাঙ্ক্ষার শিল্পসত্যরূপে।
উপন্যাস যতই অগ্রসর হতে থাকে ঔপনিবেশিকের চেতনা বহির্জগত থেকে সরে গিয়ে প্রবেশ করতে থাকে অন্তর্লোকের অনুভববেদ্যতায়, মগ্নচৈতন্য অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। মনের গহন চিন্তার অতলে ডুব দিয়ে শেকড়সন্ধানী ও আত্মানুসন্ধানী ঔপন্যাসিক গভীর উপলব্ধির ভিতর আবিষ্কার করেন ভারত সৃষ্ট কৃত্রিম বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালির হাহাকার, আর্তনাদ। বাস্তব ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে পরাবাস্তবতায় :
তখন একটা আর্তনাদ ও হাহাকার অসংখ্য চামচিকে হয়ে আকাশ ভরিয়ে তোলে। তখন দুপুরকেও রাত বলে ভ্রম হয়। রাতের আকাশকেও ভয়ঙ্কর কোনো দৈত্যের মতো দেখায়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উড়ন্ত চামচিকার ভীষণ চিৎকারে চিৎকারে পৃথিবীর কর্ণবিবর মুহূর্তেই বিকল হয়ে পড়ে। কর্ণপট থেকে ফিনকি দেয়া রক্তের ছিটে বুকের উপরে পোশাকে লাগে। একটুখানি রক্তের ছিটে একটু একটু করে জামা, টি-শার্ট, গেঞ্জি, সেমিজ, ব্রা, পেন্টি, জাঙ্গিয়া ভিজিয়ে দেয়। (২০২২ : ১৯৯)
ক্রমে রক্ত ও ঘাম অভিন্ন হয়ে উঠে। ঔপনিবেশিক চেহারা মূর্ত হয়ে উঠে লেখকের চিন্তায়, ‘ব্রিটিশদের ব্রেইন খুব সূক্ষ্ম, ওরা ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার সময় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সূক্ষ্ম হিসাব কষে বিষবৃক্ষের বীজ বুনে গেছে!’ (২০২২ : ২০০) কারণ, ইংরেজরা চেয়েছিলো ভারতবর্ষে বিভিন্ন রকম সমস্যা-সংকট স্থায়ী হোক। বিশ্বরাজনীতির পাকা কিংবা প্রাজ্ঞ খেলোয়াড় ব্রিটিশদের শাসনকালের পুরো ইতিহাস, সেই সময় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং দেশভাগ কীভাবে অনিবার্য হয়ে উঠে সেসব বিষয় একে একে স্পষ্টতর করে তোলেন রাজনীতিসচেতন ঔপন্যাসিক। তাঁর সত্যসন্ধানী চেতনা ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ অনুসন্ধানে ছটফট করতে থাকে। চলমান কাজকর্মহীন বিপর্যস্ত দিনে লেখকের মহাসত্তা দ্বিখণ্ডিত-ত্রিখণ্ডিত হয়ে পুরনো বই কিংবা উইকিপিডিয়ায়, খ্রীষ্টপূর্ব থেকে খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গ-বাংলা–বাঙালির উৎস সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠে। পুরাণতত্ত্ব, পৌরাণিক তথ্য, পৌরাণিক উৎস থেকে শুরু করে অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংলগ্ন মানুষ ও সমাজ, প্রাচ্য ও প্রাচীন বাংলা এবং নৃতাত্ত্বিক বিচারে ‘ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড), বিশ ভাগ মোঙ্গলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণে তৈরি’ বাঙালি জাতি, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তার চেতনায় ভিড় জমায়। সেইসাথে লেখকের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে বাঙালির শিল্প ও রূপক-কল্পনার যুগ-যুগান্তরের ললিত ধারা; সেই ধারায় যেমন এসে মিশেছে শাস্ত্র-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির ইতিবাচক প্রাধান্য ও সমন্বয়, তেমনি আবার দেবানুগ্রহজীবিতায় তুক-তাক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, তান্ত্রিকতা প্রভৃতির প্রতি নেতিবাচক নির্ভরতা। তবুও ইতিহাসের সাক্ষী উপমহাদেশের সভ্যতার চিহ্নসমূহ ‘পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার’, ‘অজন্তাগুহা’, ‘সিন্ধুসভ্যতা’, ‘তাজমহল’, অপার প্রাকৃতিক মহিমামণ্ডিত ‘হিমালয় পর্বতমালা’, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’, এমন-কি আমাদের ‘সেন্টমার্টিন’, ‘ছেঁড়াদ্বীপ’ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের মনে এমন এক বোধের তথা সুপারনিউমারারি সত্তার জাগরণ ঘটায়; যে ছেঁড়াদ্বীপের নীলজল অতিক্রম করে সঞ্চারণশীল কিংবা সন্তরণশীল হয়ে আরো অগ্রবর্তী হয় :
তখন ঊর্ধ্বারোহণের রূপক উত্তর দিককে পেছনে রেখে অবকাশের পরিপূর্ণতা পেতে সে আরো আরো দক্ষিণে পাড়ি দেয়, সে তখন ছুটছে, সে তখন দৌড়াচ্ছে, সে তখন সাঁতরাচ্ছে, সে তখন নোনাজলের হাঙর-তিমি হয়ে প্রশস্ত লেজে প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে দ্রুততম গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে, সে তখন ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় একটু একটু করে উদয়ের রূপক পূর্বদিকে সরে যায়, সে তখন সহস্র কিলোমিটারের বিরামহীন যাত্রায় বিরাম দিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রথমত আন্দামান ও দ্বিতীয়ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে উঠে। মৎসমানব তখন পুরোপুরি মানুষের রূপাবয়ব ফিরে পায়। তখন সে স্মৃতিবর্ধক রোগে আক্রান্ত হয়। সে তখন এক আরব বেদুঈন বালির চোখ দুটো স্পষ্টভাবে দেখে। […] তখন তার আর একটি সুপারনিউমারারি সোল একাগ্রচিত্তে বই পড়ে, বইয়ের পাতা উল্টায়, মাঝে মাঝে চশমা ঠিক করে, তখন চশমার লেন্স বা ভারী কাঁচের ভেতর দিয়ে বইয়ের কয়েকটা কিংবা কিছু কিছু বাক্য ও বাক্যাংশ বড় ও মোটা হয়ে ওঠে : জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানবসংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্যঘটে… আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। (২০২২ : ২১৪)
ঔপন্যাসিক তখন ভিন্নতর-অন্যতর-উচ্চতর এক জগতে, নিজের ভিতর নিজে, নিজের সামনে নিজে মুখোমুখি¾ এক উচ্চতর বাস্তব বা অধিবাস্তব চেতনলোকে বিচরণশীল। আদ্রে ব্রেঁত (১৮৯৬-১৯৬৬) বা অন্যান্য পরাবাস্তববাদীরা যে জগতের কথা বলেন, সে এক ‘Superreality’; যেখানে চেতনাজগতের বাস্তব ও মগ্নচৈতন্যের রহস্যসব এক হয়ে যায়; চিন্তা, কল্পনা ও স্বপ্ন মিলেমিশে যায়। (হাবিব আর রহমান, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, ২০১৪ : ২৪৮) প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে জর্জরিত, বিচিত্র কথোপকথনে অর্ধচেতন কিংবা অবচেতনের বন্ধ কামড়াগুলো যখন খুলে যেতে থাকে, উন্মোচিত হতে থাকে ‘প্রেমিকহৃদয়’, যখন খুব ক্লান্তিবোধ হতে থাকে, তখন তিনি ‘চোখ দুটি বন্ধ করেন, হয়তো ঘুমাতে চান, কিন্তু পারেন না। তাঁর চেতনাপ্রবাহে অনেক মুখ, বিচিত্র সব রং-ফুল-পাখি আর বাহারি রঙের প্রজাপতির ভীড়। তাঁর কষ্টগুলো দ্বিগুণ হতে থাকে ‘যখন পৃথিবীর সব পথ ও সব শহরকে তার কাছে একই মনে হয়’, যখন ‘সব দীঘি সব নদীকে তার একই বলে ভ্রম হতে থাকে’, যখন সব মেয়ে কিংবা সব নারী অথবা সব বালিকাকে তার একইরকম লাগে’। চরম বিরক্তি ও ক্লান্তি নিয়ে যতই তিনি প্রশ্নকর্তাকে এড়াতে চান, ততই নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, নিজের থেকে নিজেকে ছাড়ানো যায় না কিছুতেই, নিজের থেকে নিজেকে আড়াল করা যায় না কিছুতেই। সমালোচক ডক্টর শামীমা হামিদ যাকে বলতে চেয়েছেন ‘অবরুদ্ধ বিবেক’। সেই অবরুদ্ধ বিবেকের তৃষ্ণা মেটাতেই লেখককে পুনর্পাঠ করতে হয় যাপিত জীবনের বিগত অধ্যায়। পর্যবেক্ষণ করেন বাবা-মা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি নৈমিত্তিক সম্পর্কগুলো; কথকের মগ্নচৈতন্যে বিপন্নতাকে গাঢ় করে তোলে অভিযোগের পর অভিযোগ, তিনি কী আপন স্ত্রীকেই একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসেন/ভালোবেসেছেন? অন্যকোন বালিকা/তরুণীর হৃদয়ে কী কোনদিন ঝড় তুলেন নি? যে মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো¾ সেখানে কী তার কোন দায় নেই? অভিযোগ গুরুতর হতে থাকে :
ছিঃ, আপনার হৃদয়ে এতোটুকু প্রেম নেই, আপনি এতোটাই প্রেমহীন পাষণ্ড? […] আর কী-ই কথা আপানার বলবার আছে, একজন প্রেমহীন, পাষাণ, কৃপণ ও মিথ্যাবাদীর কাছে নতুন করে কী আর শোনার আছে! (২০২২ : ২৩৯)
অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। অর্থ থাকা সত্ত্বেও দিদি বা দাদিকে একটি শাড়ি না কিনে তার আকাংক্ষাকে হত্যার অভিযোগ, প্রেয়সী-স্ত্রীকে একটা জামদানি অথবা একটি মনিপুরী শাড়ি না কিনে বা কিনতে না দিয়ে শুধু শুধু হাঁটানোর অভিযোগ, কিংবা উপমহাদেশের ঐতিহ্যপূর্ণ জামদানি ও মনিপুরী তাঁত শিল্পকে অবজ্ঞার অভিযোগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন আমান্যের অভিযোগ, দূরশিক্ষণ, ইভিনিং, উইকেন্ড শিক্ষাব্যবস্থা ও অনলাইন শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ বক্তব্য দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুভূতিতে আঘাত এবং প্রকারান্তরে সর্বোচ্চ সনদ দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগ, সংবাদকর্মীদের পেশাদারিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার অভিযোগ, শান্তির প্রতীক শান্তির দূত একটি পায়রাকে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ। তিনি তখন আপন সত্তার কাঠগড়ায়। সেই মানবসত্তা ব্রেঁত যাকে বিবৃত করেন, “সত্তা হলো যাবতীয় সপ্ন, সৃষ্টি, সম্ভাবনার স্বল্পতম অন্ধকার, যেখানে মানুষের চিরন্তন রূপকল্প, মিথ এবং তার মৌল প্রতীক অতি নিঃশব্দে কাজ করে।” (পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, ২৪৯) স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের শুরুর দিকে যা ছিলো বর্ণনা কিংবা তথ্য উপস্থাপনের মতো, উপন্যাসের শেষের দিকে এসে সেই বক্তব্যগুলো আরো জোড়ালো, আরো স্পষ্ট, লক্ষ্যভেদ্য :
দুঃখ, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে, সম্ভাবনাময়ী উর্বর ক্ষেত্র আছে, কিন্তু, দারিদ্র্যমুক্ত বর্তমান নেই! সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, সবকিছুতেই রাজনীতিকরণ আর বিভেদ সৃষ্টির মানসিকতা এবং জাতীয় ভিশন, মিশন, ইউনিটি ও কনসিসটেন্সি তৈরিতে নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতার কারণে আমাদের সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুর্গতি! আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আছে, অথচ সুষম সচ্ছলতা নেই; আমাদের বিবিধ প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান আছে, অথচ কোথাও শতভাগ স্বচ্ছতার প্রচেষ্টা নেই; আমাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে, অথচ যথোচিত মূল্যায়ন নেই; (২০২২ : ২৫৪)
‘যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ করেও সার্টিফিকেটহীন, শুধুমাত্র এক টুকরো প্রত্যয়নপত্রের দাবিদার দাদুটি বড্ড অসহায় তার প্রজন্মের সামনে’; নাতি তখন সত্যানুসুন্ধানী হয়ে আর একবার লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখে, ঔপন্যাসিকের ভাবনায় তখন আন্দোলন-বিদ্রোহ শব্দগুলো বিবৃত হয় এভাবে :
আন্দোলন এক অর্থে কম্পন। অনুক্ষণের শ্বাস-প্রশ্বাস। আর-এক অর্থে আলোড়ন। প্রাত্যহিকের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম। বোধকরি দুটোই হচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াই। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রতিক্ষণ লড়াই করে; এবং লড়াই করেই তাকে বাঁচতে হয়। জীবনের সঙ্গে তাই আন্দোলন অবিচ্ছেদ্য। […] আভিধানিক অর্থে দ্রোহ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তবে, ন্যায় ও অন্যায়ের ধারণা ব্যক্তি, সময় ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা নির্বিশেষে স্থির বা এক নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ বিধি-বিধান ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, না-কি অভিজ্ঞতাপুষ্টির মাদক-মন্ত্রে সমাজ-ব্যক্তির স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও অধিকারকে অপহরণ করে, এমন দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় দেশ-কাল-সমাজ এগিয়ে চলে। আর, এই দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার সূত্রায়ণ ঘটে একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্যিক হৃদয়-ভূমে। হৃদয়বৃত্তি প্রাথমিকভাবে জারিত হয় বৌদ্ধিক-মস্তিষ্কে এবং স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে এবং ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয় দ্রোহ বা বিদ্রোহে। (২০২২ : ২৬২-২৬৩)
লেখকের চৈতন্যপ্রবাহে স্বপ্ন আর বাস্তবতা তখন আরো কাছাকাছি হতে থাকে। বাস্তবের বৃহৎ চত্বরে রাতের শহরে চিরচেনা পথ ধরে তিনি হাঁটতে শুরু করেন, উপলব্ধি করতে থাকেন কতো পরিবর্তন ঘটে গেছে :
নদীটা হারিয়ে গেছে। ছোট হতে হতে বিলীন হয়েছে নদী, আকাশ, বৃক্ষ ও মানুষগুলো। হ্যাঁ। বনসাই দখল করে নেয় পৃথিবীর চাকচিক্যময় স্থানগুলো/ বৃক্ষহীন স্থাপনাগুলো সবুজ হয়ে ওঠে কৌটার রঙে/ নতুন পৃথিবীতে নতজানু হয় প্রকৃতি/ নতজানু প্রকৃতির সন্তান/ মানুষ হয় খর্বাকৃতি! তিনি তখনো হাঁটতে থাকেন। (২০২২ : ২৬২)
এভাবেই চলতে থাকে ঔপন্যাসিকের চেতন-অবচেতন-অর্ধচেতনের অফুরন্ত অনুভূতির শব্দময় প্রকাশ। শব্দের পর শব্দ থরে-বিথরে সাজিয়ে কথার যে পিরামিড নির্মাণ করেন শব্দের বিন্যাস-কৌশল, ধ্বনিব্যঞ্জনা, জাদু আর বাস্তবতার মিশেলে, তা পাঠককে যেন মোহাবিষ্ট করে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং সেইসাথে রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিতময়তায় ভাষা হয়ে উঠে অনুভববেদ্য। তাই ব্যক্তিত্ব এবং দ্রোহের সংজ্ঞায় ঔপন্যাসিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন ‘কাক’; গোষ্ঠীবদ্ধ কাকের ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন :
কাক কী কখনো পাখি হয়! কেনো হবে না, ওর কি ডানা নেই? ডানা থাকলে কী পাখি হয়! কেনো, ও কি ডিম পাড়ে না, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায় না? ডিমে তা দিয়ে খোলোস ভেঙে বাচ্চা ফুটালে বুঝি পাখি হয়! কেনো, ওর কি চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড আর উচ্চ কোষীয় জৈব-রাসায়নিক হার আর হালকা অথচ মজবুত হাড় নেই? সবকিছু আছে, কিন্তু কাক পাখি নয়, কাক কাকই, (২০২২ : ২৬৪)
মানুষও তাই। এ-প্রসঙ্গে ডক্টর শামীমা হামিদের বিশ্লেষণ :
মানুষও তো তাই! একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি আর ঘোলা সংস্কার নিয়ে সার্বিক বিশ্বস্ততা পেলেও পূর্ণ ও সামূহিক মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হতে হয় মানবিকতার গুণে; অথচ সেই গুণ আজ বিনষ্টির শেষ ধাপে! লেখকের প্রতীক হয় ‘বানর এবং ডুগডুগিওয়ালা’¾ নাচুনী বানর যেমন ডুগডুগির তালে নাচে, ইশারায় তুলে ধরতে চায় সামাজিক অব্যবস্থাপনার চিহ্নগুলো; কিন্তু তাকে যে নাচায়, সেই ডুগডুগিওয়ালা বাজিকর সে নিজেও তো ক্রমশ গলে যাওয়া একজন মানুষ। সমাজটা তাহলে কিসের দখলে, জনগণইবা কে, কাদের? পাতার পর পাতা জুড়ে সে বর্ণনাও দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। (শামীমা হামিদ, ‘বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি : নিমগ্ন-চেতনায় শব্দযাত্রা’, ২০২৩)
আসলে লেখকের মগ্ন মানস যে বিশ্বাস আর আবেগকে ধারণ করে আছে¾, তারই অনিবার্য প্রকাশ ঘটে পরবর্তীতে:
কিছুক্ষণ পর অন্ধকারের ভেতর ভাবতে থাকি, কোথায় একটা তার ছিঁড়ে গেছে, নয়তো তাল কেটে গেছে, মানুষ খেই হারিয়ে ফেলেছে। সবাই ছুটছে, ছোটাছুটি করছে, ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে যেতে চাইছে। যেভাবেই হোক তাকে সামনে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। এগুতেই হবে। শুধু এগুলেই হবে না, বাহবা অর্জন করতে হবে, শুধু বাহবা ও হাততালি নয়, রায়বাহাদুর অথবা বীরবাহাদুর অন্তত কোনো একটি খেতাব অর্জন করতেই হবে, আধুনিক সমরসজ্জিত কমরেড কিংবা কর্নেল হতেই হবে এবং সেজন্য তাকে সবুজ শৈশব সহজ খেলনা ছেড়ে দৌড়াতে হবে, কৈশোরের কমলা রোদগুলোকে আড়ি দিতে হবে, বন্ধুত্বকে অস্বীকার করতে হবে, ভুলে যেতে হবে লাটাই-ঘুড়ি, রঙিন কাগজ, কাগজের নৌকা, বাঁশের বাঁশি, কাঁঠাল ও কাগজি লেবুর ঘ্রাণ। আবার ভাবি, কে ছুটছে, কেউতো ছুটছে না, সকলেই ছোটাছুটির মতো করে একটি চক্রাবৃত্তে ঘুরছে! (২০২২ : ২৭০)
এই চক্রের শামিল হয়ে পতিত পণ্ডিত পুরোহিতের গান গাইতে হবে, বাজার উপযোগী দেবভাষায় বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে হবে, জীবনের সঙ্গে ছল করে দুগালে রঙ মেখে বাকি সময়টায় এভাবে নৃত্য করতে হবে ভেবে লেখকের খেদ হয়, নিরুপায় ও অসহায়বোধ হতে থাকে, আধুনিক সভ্যতা নিয়া মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে, ‘পৃথিবীতে এখনো আধুনিক গডো আসেন নি?’ অসহায়ত্ব, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করতে থাকে, বিচ্ছিন্নতা চরম হতে থাকে, আপন প্রেয়সী-স্ত্রীও তখন দূরতম মেঘবালিকা’¾ এই বিচ্ছিন্নতা বা শূন্যতার ‘সঙ্গে অ্যাবসারডিটির কল্পনা করতে পারি, যে অ্যাবসারডিটির কথা আলবেয়ার ক্যামু তাঁর দি মিথ অব সিসিফাস (১৯৪২) গন্থে প্রথম প্রয়োগ করেন। ‘এক্ষেত্রে মানুষ যেমন অসহায় হয়, তেমনি জীবন ও চলত-শক্তিহীন হয়ে পড়ে। (পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক, ২৮১) লেখকের চিন্তাগুলো উদ্ভট, অদ্ভুত হতে থাকে, আধোঘুম ও আধোচৈতন্যের ভেতরে বিভ্রান্তবোধ হয় :
সে ক্রমশ চিৎকার করছে এবং পড়ে যাচ্ছে এবং পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে। একপর্যায়ে সে আর শ্বাস নিতে না পেরে চিৎকার করতেও পারছে না। হাত-পা-চোখ-মুখ বাঁধা কোনো আতঙ্কিত প্রাণির মতো সে শুধু ছটফট করছে। চাপা কিংবা বোবা আর্তনাদ করছে। সে পড়ে যাচ্ছে। সে যেনো তলিয়ে যাচ্ছে। সে যেনো শ্বাস নিতে না পারায় নিশ্চিত মারা যাচ্ছে। যদিও সে বুঝতে পারছে না যে, সে জীবিত রয়েছে, না-কি মারা গেছে? সে নিদ্রায় আছে, না-কি পূর্ণ জাগরণে রয়েছে? সে এখন মর্ত্যলোকে, না-কি পাতালপুরীতে রয়েছে? সে এখনো মেঘরাজ্যে, না-কি বিছানায়? (২০২২ : ২৮৩)
অবসাদ ও উত্তেজনার ভেতর-কল্পনা ও বাস্তবের রেখা তখন মুছে যেতে থাকে¾, প্রজাপতি থেকে চড়ুইপাখি, তারপর কবুতর, তারপর মানুষ :
আচ্ছা, প্রজাপতি যদি চড়ুই হয়, চড়ুই যদি কবুতর হয়, তাহলে, কবুতর কি মানুষ হতে পারে না? কেনো হতে পারে না, অবশ্যই পারে। পারবে। তাহলে, সম্মুখে উপবিষ্ট কবুতরটি কি কোনো মানুষ? উড়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে ফেলা অথবা দূরে থাকা নতুবা মৃত্যু হওয়া নয়তো অভিশপ্ত কোনো মানব কিংবা মানবীর রূপান্তরিত নয়তো বিবর্তিত নতুবা ক্ষয়িষ্ণু রূপ! সে কবুতরটিকে নিরীক্ষণ করে। […] যেনো কবুতরটি সহস্র বছরের বিরহ-বেদনার নোনাজল আড়াল করে অতি নীরবে তার পানে চেয়ে রয়েছে। তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত কবুতরটি হয়তো তাকে কিছু বলতে চায়। হয়তো কিছু বলতে চায় না, তার কাছে ওম চায়, ভালোবাসার ওম। তখন সে মায়া অনুভব করে। তার মধ্যে প্রেম জেগে উঠে। দুই হাতে দুই ডানা ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু দেয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে হাত বাড়ালে কিংবা বিছানায় উঠে বসলে অথবা বিছানা ছেড়ে উঠবার মুহূর্তে হঠাৎই কবুতরটি উড়ে যায়। আর, তখনই ঘরে প্রবেশ করে একটি নারী। তার প্রেয়সী-স্ত্রী। (২০২২ : ২৮৪)
স্পষ্টতই পাঠক মাত্রই ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, জ্ঞান, দর্শন, স্বপ্ন, ভ্রম, সংস্কার কিছুই আসলে কাল্পনিক কিছু নয়; বরং জীবন-জগত-মানুষ যে বিশেষ রূপে উঠে আসে উপন্যাসে, তা কাল্পনিক হলেও স্ব-কাল ও স্ব-সমাজ নির্ভর গভীর ভাবনাপ্রোথিত। আর সাহিত্য তো জীবনের-ই কথা বলে, ‘সাহিত্য জীবনের রস রূপায়ণ, সকল প্রকার শিল্পসাধনা জীবনভাবনারই প্রতিরূপ।’ (ড. ফরিদা সুলতানা, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা, ১৯৯৯ : ১)
উপন্যাসের সমাপ্তি কথকের মতোই পাঠককেও এক গভীর ভাবনায় পতিত করে এবং এক গভীর জীবনবোধ তৈরি হয়¾, যখন জানতে পারি কথকের মতো তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর শরীরেও করোনার উপসর্গগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে; অর্থাৎ, হয়তো দুজনেই করোনাক্রান্ত কিংবা না হলেও আশঙ্কাচূড়ান্ত¾, জীবনের সেই চরম সত্য, চরম অনিশ্চয়তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে; জীবনযুদ্ধ থেমে যায় নি¾ তবুও নতুন একটা ভয় কিংবা সাহস। ‘সাহস’¾ এই সাহস জীবনের, জীবনসংগ্রামের¾ লড়াইয়ের, বাঁচার¾ বেঁচে থাকার¾ : ‘মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে এবং যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকবে। […] জীবন হারতে হারতেও জিতে যায়। জীবন জিততে জিততেও হেরে যায়। কিন্তু জীবন নিঃশেষ হয়ে যায় না। (২০২২ : ৫০) যে উপন্যাসটির শুরু হয়েছিলো মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে, সেই উপন্যসের পুরোটা জুড়ে লেখক মূলত বাঁচার তথা বেঁচে থাকার গল্পই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আবেয়ার ক্যামুর দি প্লেগ এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (১৯২৭-২০১৪)-এর লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা (১৯৮৫) এই উপন্যাস দুটি স্মরণযোগ্য। দুটি উপন্যাসই শুরু হয়েছে মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে :
Perhaps the easiest way of making a town’s acquaintance is to ascertain how the people in it work, how they love, and how they die. (Albert Camus, The Plague, translated from the French by Stuart Gilbert, 1948 part-I)
গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা উপন্যাসেও শুরুতে রয়েছে একটি মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা¾; ডা জুভেনাল উরবিনো সেই বিবর্ণ মৃত্যুদৃশ্যে উপস্থিত থেকে ভাবছেন :
Dr. Juvenal Urbino had often thought, with no premonitory intention, that this would not be a propitious place for dying in a state of grace. (Grabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera, Translated from the Spanish by Edith Grossman, 1988)
কেন শুরুতেই মৃত্যুর বর্ণনাই এসকল উপন্যাসে উঠে এসেছে? হতে পারে¾ অনিবার্য সত্য ‘মৃত্যু’¾ মহামারীর সময়ে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠে বলে, কিংবা, হতে পারে এই মৃত্যুর মিছিল সৃষ্টিশীল মানুষের মনকে আলোড়িত করে তোলে বলে¾; মূলত মহামারীই তৈরি করে এই প্রেক্ষাপট। মহামারীকালীন জীবনবাস্তবতা সৃজনশীল মানুষদের নতুন করে ভাবায়, আর তাই জীবনের গল্প বলতে গিয়ে তারা পেয়ে যায় নতুন প্লট।এবং সাহিত্যের পাতায় তাদের প্রচেষ্টা অমর হয়ে থাকে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। আমরা দেখেছি করোনা শুরু হওয়ার পর থেকেই করোনার প্রেক্ষাপটে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে; শুধু তাই নয়, বিশ্বসাহিত্যের মহামারী-অতিমারী নিয়ে লেখা সাহিত্যগুলোও নতুন করে আলোচনা-সমালোচনায় এসেছে। কিন্তু, মহামারী নিয়ে লেখা সব সাহিত্যই কী কালজয়ী হয়ে উঠে? নিশ্চয়ই নয়। যেকোনো সাহিত্য কালজয়ী হয়ে উঠে তখনই, যখন সেখানে থাকে গভীর জীবনবোধের প্রকাশ। ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্সের বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে এই প্রয়াস ছিলো লক্ষণীয়।
আবেয়ার ক্যামুর দি প্লেগ মোটেও কেবল মহামারী প্লেগ নিয়ে নয়; গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা যতোটা না মহামারী নিয়ে, তার চেয়ে বেশি এক আশ্চর্য জীবন্ত ভালোবাসার গল্প হয়ে উঠে। মাওলা প্রিন্সের বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসেও দেখতে পাই মহামারী একটা উপলক্ষ মাত্র; যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জীবনের সমগ্রতাকে ধরতে চেয়েছেন। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি জীবন-সময়-সমাজ-রাজনীতিকে দেখেন নি, দেখাতেও চান নি। সামূহিক মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন দেখানোর সাধনায় নিমগ্ন ঔপন্যাসিক সমগ্রটা দেখেছেন ও সমগ্রটা ভেবেছেন এবং সমগ্রটাকেই দেখাতে চেয়েছেন।
তথ্যপঞ্জি :
ফরিদা সুলতানা (১৯৯৯) : বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা । ঢাকা।
বিনায়ক সেন (১৪২৭) : ‘সাহিত্য, অতিমারী ও সমাজ’। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা । খণ্ড ৩৮। ঢাকা।
মাওলা প্রিন্স (২০২২) : বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি । নৈঋতা ক্যাফে। ঢাকা।
রফিকউল্লাহ খান (২০০৯) : বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ । ঢাকা।
রেজাউল করিম রনি (২৮ আগস্ট ২০২০) : ‘ঘটনা ও সত্যের সম্পর্ক : করোনার পরে সাহিত্য’। সাহিত্যসাময়িকী, যুগান্তর : আজকের পত্রিকা । ঢাকা।
শামীমা হামিদ (এপ্রিল ২০২৩) : ‘বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি : নিমগ্ন-চেতনায় শব্দযাত্রা’। ওয়েবম্যাগ অনুধ্যান । নেত্রকোণা।
স্বপ্না রায় (২০০৬) : বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা ।কলকাতা।
হাবিব আর রহমান (২০১৭) : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক । ঢাকা।
Albert Camus (1948) : The Plague, translated from the French by Stuart Gilbert.
Grabriel Garcia Marquez (1988): Love in the Time of Cholera, Translated from the Spanish by Edith Grossman.


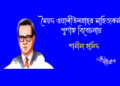








Discussion about this post