তাহমিনা আক্তার দিথী
১.
একটা ক্রান্তিকাল, এলোমেলো ভাবনার মেলা, মৃত্যুচিন্তা, ভয়, শাসন কিংবা শোষণ; অন্যদিকে জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন দেখা, ফিনিক্স পাখির মতোই মৃত্যু মেরে বেঁচে ওঠা; —এমনিই এক অনন্য আখ্যান “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি”। যুদ্ধটা বেঁচে থাকার, নিজের সাথে, সময়ের সাথে। যুদ্ধটা ব্যক্তি কিংবা দেশ-কালের ক্ষুদ্র গণ্ডি বা সীমানা পেরিয়ে গোটা বিশ্বের, ব্যষ্টির থেকে সমষ্টির; ক্রান্তিকালকে পিছনে ফেলে শূন্য থেকে শিখরে আরোহনের।
মানুষ মূলত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে, একটু শান্তি পেতে, মুক্তির আকাশে প্রাণ ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে। তাই বেঁচে থাকার জন্য কিংবা বাঁচার মতো বাঁচতে লড়ো, লড়ে যাও, যুদ্ধ করে টিকে থাকো এবং শান্তি ছিনিয়ে আনো— সময়ের এমনই এক প্রত্যয় প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাওলা প্রিন্সের “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের আখ্যানও তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের সীমানা ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক। সময় এখানে ত্রিকালদর্শী। শ্বাস না ফেলা বিরামহীন এক আখ্যান দিয়ে ঔপন্যাসিক নিরন্তর চলতি পথের সংগ্রামকেই যেন কলমের ডগায় নতুন এক নির্মিতি দিয়েছেন। কিছু আশা-নিরাশা, শোষণ-যন্ত্রণা, ক্রান্তিকাল, আর্থসামাজিক বাস্তবতা, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে গোটা বিশ্বের রূপ নির্মিতি—, সর্বোপরি এক মানবজনমকে ভাবে-ভঙ্গিমায় প্রকটিত হতে দেখি এই উপন্যাসে। প্রচ্ছদের ডিফেন্স থিওরির আর্ট স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয়— “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি”।
২.
উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে করোনা মহামারীর ভয়াল দিনগুলোর এক আতঙ্কগ্রস্ত মৃত্যচিন্তা দিয়ে। এই বুঝি আজরাইল ডাক দিলো, পৃথিবীর সব মানুষ নেমে এলো মৃত্যুচিন্তায় সর্বদা তটস্থ থাকার কাতারে। এই মৃত্যুপুরীতে আজরাইল কখন, কাকে, কোন বয়সে নিয়ে যাবে তা কেউই জানে না। করোনা মহামারী এই মৃত্যকে যেন আরো কাছ থেকে অনুভবের সুযোগ করে দিলো পৃথিবীকে। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে, “এখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন-ই হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আওয়াজ; সমষ্টিগত জনগোষ্ঠীর নিদারুণ কণ্ঠস্বর!” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৮৭) উপন্যাস-কথকের পারিবারিক কবরস্থানের চিত্রায়ণও যেন এই মৃত্যচিন্তাকেই বারবার মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু, এতো এতো মৃত্যুর মাঝেও মানুষের মৃত্যুকে বরণ করতে না চেয়ে বেঁচে থাকার যে অদম্য ইচ্ছা—, সেই আশাজাগানিয়া বেঁচে থাকার গান আমরা উপন্যাসে প্রকটিত হতে দেখি :
তবে কী পৃথিবী ধ্বংস হতে আর বেশি দেরি নেই? স্বর্গ কিংবা নরকের ট্রেন অথবা নৌকা তাহলে কী দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়? কোন্টে বায়, আইসো ক্যা, আইসো সবায়; কিন্তু, আমরা তো যেতে চাই না, আমরা তো এখনো প্রস্তুত নই, প্রস্তুতি নিই নি!… হামাক ক্ষমা করো বাহে, হামরা তুমার সাতে যাবার নই, হামরা তুমার পাছোত্ তুমার সাতোত্ যাবার নই…। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৪৯)
করোনাকালে মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন থাকা কথকের স্মৃতিচারণে ও ভাবনা-চিন্তায় উঠে আসে কোভিড-১৯ কে ঘিরে ক্ষমতাধর দেশের বৈশ্বিক কূটনীতি, করোনার উত্তেজনা, অবসাদ, লকডাউন, সরকারসহ সকল পর্যায়ের মানুষের অসচেতনতা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাবে জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক তথা মৃত্যুর প্রতীক্ষারত মানুষের দুর্দশার চিত্র, পারিবারিক বিষয়াশয়-খুঁনসুটি, প্রেমচেতনা, শিক্ষাভাবনা, দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি-ঐহিত্য-অর্থনীতি এবং রাজনীতিসহ নানা বিষয়।
৩.
ঔপন্যাসিক তথা কথকের জন্ম, বেড়ে ওঠা, জীবনযুদ্ধে হাল না ছাড়ার দৃঢ় প্রত্যয়, শৈশবের স্মৃতিচারণ, ছোটবেলায় শব্দবিভ্রাট, পারিবারিক খুঁটিনাটি, দাদি-নাতি অথবা স্বামী-স্ত্রী কিংবা পিতা-পুত্রত্রয়ের খুঁনসুটির চিত্র, সন্তানের প্রতি কথকরূপী বাবার স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা, পরিবার ও স্বজনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, পারিবারিক টানাপোড়েনের চিত্রসহ পারিবারিক নানা বিষয় অসাধারণ পারঙ্গমতায় রূপায়িত হয়েছে “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” উপন্যাসের সামগ্রিক পরিসরে। মায়ের সাথে কথোপকথনকালে মায়ের স্মৃতিচারণে উঠে আসে লেখকের জন্মের ইতিহাস :
তুই হইছিস রাইতের ব্যালা, সারাদিন উপ্যাস থাকি প্রথমে ধান সিদ্ধ করি সেই ধান ডেকচিত্ ভাজি তারপর সইন্ধ্যার সমায় সেই ভাজা ধান উড়ুন-গাইন দিয়্যা বাড়া বানি চাইল করি তারপর সেই চাইলে ভাত রান্না করি রাইতোত্ খ্যায়া শুইলাম, কিছুক্ষণ পর প্যাটের ব্যতা উঠিল, আর, কিছুক্ষণ পর তুই হলু, অন্ধকার ঘর আলো করি তুই আসলু, তখোন দিনের কষ্ট আর রাইতের ব্যতা সব চলি গ্যালো, বুক জুড়ায় গ্যালো, বুকটা বরফ-আইচক্রিমের মতোন ঠাণ্ডা হইল্ ! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১১১)
দাদি তথা দিদিকে বুদ্ধিমতী ও অহমবোধসম্পন্ন স্বশিক্ষিত নারী বলেছেন লেখক। পুত্রবধূকে লেখাপড়া করানোয় দাদির বিচক্ষণতা যেমন প্রকাশ পায়, বিপরীতভাবে প্রকটিত হয়েছে ছেলের বিয়ে ধুমধাম করে দিতে না পারা এবং পুত্রবধূর বাড়ি থেকে উপঢৌকন না পাঠানোয় দাদির আফসোস, চিরায়ত বউ-শাশুড়ির সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথা। দাদির হাতে মায়ের মার খাওয়ার ঘটনায় শাশুড়ির অত্যাচারের নির্মম চিত্রও পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না :
এমন অনেকগুলো সম্ভাবনার কোনো একদিন তার বাবা বা আব্বু অফিসে চলে যাওয়ার একটু পরেই বধূ-শাশুড়ির কলহ শুধু হয়, হবে, হয়েছিলো এবং যার পরিণতিতে পুনরায় শোনা যাবে বা যায় একটি চিৎকার, ও মা, ও মা, ও মা; কী বিকট চিৎকার; যেনো কোনো কিশোরী কিংবা সদ্য যৌবনা কোনো মেয়েমানুষ দৈত্য বা ডাইনির হাতে ধরা পরে মুক্তির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তার ঘুমন্ত বোবা-কালা-বধির মাকে জাগ্রত করতে চাইছে। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১০৬)
মায়ের স্কুলে যাবার কথা, মেট্রিক পাশ করেও ঘুষ দিতে অপারগ হওয়ায় চাকরি না হবার প্রসঙ্গ, দাদির অত্যাচার-নির্যাতন, ভাত-কাপড়ের কষ্টের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে সংগ্রামশীল এক নারীর বেঁচে থাকার তীব্র লড়াইয়ের চিত্র :
তখন কিংবা অন্য এক সময়ে মা বলবে, বলবেন, আমাদের জীবনটা হইলো কুত্তা-বিড়ালের জীবন, টানি-টানি ছেঁচড়ি-ছেঁচড়ি চলা জীবন, প্যাটোত্ পাথর বান্দি ত্যানা-কাপড় পরি ধাকরি-ধুকরি কোনোমতে বাঁচি থাকার জীবন; বাপের সংসারে শান্তি পাই নাই, ভাত থাকিয়াও ভাতের কষ্ট পাইছি, স্বামীর বাড়িত্ আসিয়্যাও কষ্ট; এ্যাটে খালি ভাতের কষ্ট নয়, ভাতের সাতে কাপড়েরো কষ্ট! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১১১)
স্মৃতিচারণে আমরা দেখি, মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রথম চাকুরিতে নিয়োগ পান কথকের পিতা। তারপর বিদেশী এনজিওতে চাকুরি করেন। পিতার সাথে কথকের নানা স্মৃতিচারণ উপন্যাসে প্রকটিত হয়েছে। রসবোধের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের সুগভীর বেদনার উপস্থাপন ঘটে ঈদে পিতার ছোট ভাইকে পোশাক কিনে না দিতে পারার ঘটনায় বড় ভাই তথা কথকের হাস্যরস মেশানো কথায় :
আমার ছোট ভ্রাতা ঈদের দু-একদিন আগে কেঁদেছিলো নতুন পোশাকের জন্য, সেবার অবশ্য আমি কাঁদি নি, কাঁদার বয়স পেরিয়ে গিয়েছিলো বলে হয়তো খুব হেসেছিলাম, হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আব্বুর কী দোষ, বলো, আব্বু তো জানতো না যে ঈদ আসছে, সামনে ঈদ, গতকাল অফিস শেষে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই শুনতে পেলো যে আগামীকাল ঈদ, হি-হি-হি! ( মাওলা প্রিন্স, ২০-২১)
পারিবারিক কথার সূত্র ধরে আসে নানা-নানির বিয়ের ইতিহাস। কথকের নানা নানিদের বাড়িতে লজিং থাকতো। নানির বিয়ে ভেঙে গেলে সে রাতেই নানা নানিকে বিয়ে করে। নানির মায়ো তথা দাদিশাশুড়ির খেপানোতে ক্রুদ্ধ হয়ে নানার দ্বিতীয় বিয়ের কথাও আমরা জানতে পাই। নানির স্মৃতিচারণে আমরা দেখি, নানুর (নানার) নানিকে রেখে অন্য বিয়ের পর ৪০ বছরে মাত্র ৩ বার নানির সাথে নানুর দেখা হয়েছিলো। শেষবার দেখা হয়েছিলো নানি মারা যাবার অন্তিম মুহূর্তে, যাকে লেখক তুলনা করেছেন “কৃষ্ণকান্তের উইল” উপন্যাসের ভ্রমর আর গোবিন্দলালের সাথে : “ভ্রমরের সতীত্ব ও নিখাদ ভালোবাসা যে পরনারীতে রূপজ মোহাবিষ্ট হয়ে গৃহত্যাগী স্বামী গোবিন্দলালকে তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কাছে টেনে এনেছিলো, তার পুনঃদৃশ্যায়ন দেখি নানি ও নানুর বিচ্ছেদে ও চিরবিদায়ে।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৩২)
জনকন্ঠে সাংবাদিকতা করা কথকের মামার এরেস্ট হবার ঘটনায় উঠে আসে সাংবাদিকতা পেশার নানা প্রতিকূলতার কথা। নানু বলেছিলেন— সাংবাদিকতা হলো সাংঘাতিকতা। স্বার্থের খাতিরে কিংবা সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে সংবাদপত্রে রং চটিয়ে সংবাদ পরিবেশনের আড়ালে যে সত্য চাপা পড়ে যায়, সে দিকটি লেখকের বর্ণনায় পরিস্ফুটিত হয়। পত্রিকার উপযোগিতাকে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু, ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা থাকতে হবে, ভালোটুকুকে গ্রহণ করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কথকরূপী লেখক কবিতা লেখে শুনে মামা বলেছিলেন, নিজের প্রতিভাগুলোই একসময় অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, যে প্রতিভার জন্য আমরা বর্তমানে আনন্দ পাই, তা-ই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় আর এক সময়ে। মূলত আত্মপ্রতিষ্ঠা না পাওয়ার অন্তর্জ্বালা আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা মানুষকে যে প্রতিভাবিমুখ বা প্রতিভাবিদ্বেষী করে তুলে, তারই প্রকাশ ঘটেছে মামা চরিত্রের কথকতায়। কিন্তু কথকরূপী লেখকের দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো মামার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবার। উপন্যাসে শৈশবের বর্ণনায়ও উঠে আসে লেখকের নিজেকে তৈরি করার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা :
এই ছেলে যতোই কথা কম বলুক, এই ছেলে যতোই চুপচাপ থাকুক, এই ছেলেকে বাহিরে যতোই ডেকি মুরগির মতো মনে হোক না কেনো, বস্তুত, ও মোরগ; ভেতরে ভেতরে ও একটা টগবগে মোরগ, ওর ভেতরে সব সময়েই একটা বর্ণিল তাগড়া মোরগ ডাক দেয় কোক্কুরুৎ; ঐ ছেলে হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে না, মোরগের মতো কোক্কুরুৎ কোক্কুরুৎ করে বাঁকে! সে অপেক্ষা করে; অপেক্ষা, অপেক্ষা, আর, অপেক্ষা। সে নিজেকে তৈরি করতে চায়; তৈরি, তৈরি, আর, তৈরি। সেই ছেলে অদৃশ্য ছুরি কিংবা কাচি কিংবা খন্তা কিংবা কুড়ালে শান দেয়; শান, শান, শান। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১০৮)
শেষ পর্যন্ত তিনি যে নিজেকে যথার্থরূপে তৈরি করতে পেরেছেন, নিজের প্রতিভায় অনবরত ঠিকমতো শান দিয়ে পেরেছেন, সে-কথাও আমরা উপন্যাসে পাই।
৪.
উপন্যাসের আখ্যানে রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে উঠে আসে ভারতবর্ষ শাসনের ইতিহাস। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলন, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি ও বাংলার ইতিহাস, উৎপত্তিসহ রাজনৈতিক নানা বিষয়কে যুক্তিতর্ক দিয়ে অসাধারণ পারঙ্গমতায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। যেকোনো দুর্যোগে সরকার যে পরিমাণ আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে থাকে, তা যদি সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যায় তবে জীবন ও জীবিকা এতো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু, যেখানে হিল ক্লাইম্ব খেলার ঘোরে একটা বাচ্চা মোহগ্রস্থ হয়ে নিজের ছোট সহোদরের কাছে বাহনা দিয়ে বেশি খেলতে চায়, সেখানে রাজনীতির ইঁদুর দৌড়ে সবাই এগিয়ে যেতে চাওয়াটাই যে স্বাভাবিক—, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কথকের কথায়। রাজনীতির এই ইঁদুর দৌড়ে শোষক কিংবা ক্ষমতাসীন উপর মহলের শোষণের কালো থাবায় জর্জরিত ও শোষিত পৃথিবীর অসহায় আপামর মানুষগুলো, যার প্রতীকী রূপায়ণও উপন্যাসে উঠে আসে :
শুরু হলো ঐ তর্জন-গর্জন-বর্ষণ, ছাদে ছাদে মাঠে মাঠে পথে ঘাটে শুধু শকুনের ছায়া, পৃথিবীতে আজ মৃত মানুষের মাংসখেকো মহাশকুনের মহা-উল্লাস—! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৩৭)
এ শকুন যেন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখা শোষক সমাজ। উপন্যাস-কথকের তিন পুত্রের কথা ধরে আসে বিশ্বরাজনীতির কথা। যে দেশে রাষ্ট্রপতির চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা বেশি, সেখানে আব্রাহাম লিঙ্কনের ডেমোক্রেসি যেন ঘুমিয়ে যায় রাজনীতির বেড়াজালে। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাস ঘাটলেও আমরা দেখি, ভারতবর্ষের যে রাজনীতি তা মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত শাসকের বদলে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাওয়া শাসকেরা এখানে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছে। ঔপন্যাসিক এই রাজনীতিকে তুলনা করেছেন বাজিগরের বানরখেলা দেখানোর সাথে :
অতীতে যারাই যে খেলা দেখাতে এসেছিলো তারাই ছিলো ধান্দাবাজ, কী করে অন্যের পকেট কাটা যায়, কী করে অন্যের টাকা নিজের পকেটে পুরে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়, কী করে বাবা-দাদার ধর্মে আর গ্রামবাংলার ঐতিহ্যে চুনকালি মাখিয়ে বিদেশী বিধর্মী নারী-পুরুষ নিয়ে ফস্টিনস্টি করা যায়, কী করে জনগণ ও দর্শক-সমাজকে খেলার নামে জুয়ার আসরে আটকে রেখে তাদেরকে বিদ্যাবুদি্ধর চর্চা থেকে বিরত রাখা যায়, এইসব ছিলো তাদের আসল খেলা, আসল মতলব; কিন্তু, আমি ঐসব খেলা দেখাই না, ঐসব খেলায় আমার মরহুম আব্বাজানের নিষেধ আছে, আমার স্বর্গবাসী গুরুজির কঠিন মানা আছে, আমি শুধু ঐতিহ্যবাহী বানরের খেলা দেখিয়ে জনগণকে আনন্দ দেই, জনগণের অন্তরে সুখ ধরাই, জনগণের জীবনযাত্রায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৬৯)
রাজনীতি তথা ক্ষমতা যার বা যাদের দখলে থাকে সে বানরনাচ দেখানোর মতো করেই জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। জনগণ আশ্বস্ত হয়, মুগ্ধ হয়; কিন্তু, ক্ষমতা ভোগ করে উপর মহলের লোকেরাই, তথাকথিত বানর নাচের মূল রশি যার হাতে থাকে। যার হাতে রশি তার কথায় লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন ব্যঙ্গের তীক্ষ্ম অনুভূতি :
সুধীবৃন্দ, আপনাদের প্রদেয় এই বিশাল অর্থের একটা কড়িও আমি নিবো না, এর একটি কানাকড়িও আমার পেটে যাবে না, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই বিশাল অর্থ দিয়ে আমি আজীবন এই বানরের সেবা ও পরিচর্যা করবো, আগামী দিনের কথা ভেবে, আমাদের ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা মাথায় রেখে, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আনন্দ মজুদ রাখবার প্রয়োজনে বানরের প্রজনন খামার গড়ে তুলবো, (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৭০)
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই বানর মূলত গুরুত্বপূর্ণ পদে ক্ষমতাসীন শাসকদল তথা পলিসি মেকারদেরই প্রতীকী রূপায়ণ। নিজেদের স্বার্থে পলিসি মেকাররা নিত্যনতুন পলিসি মেক করে, আর সারা দুনিয়ার হাপিত্যেশ করা হাভাতে মানুষজন ওদের পিছনে দৌড়ায়। রাজনীতির চাকার ঘোরপ্যাঁচে উপন্যাস-কথকের মামার জীবনের বৃত্ত পাল্টে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনায় রাজনীতির এই খোলস উন্মোচিত হতে দেখা যায় : “প্রভু রাজনীতি কী? রাজসিংহাসনের নিমিত্তে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতি।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৯৪) স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের পক্ষে নিয়ম-কানুন করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার দক্ষতাই যেন রাজনীতি। মানুষ যেখানে পণ্য। যেখানে পৃথিবী শাসকরূপী শোষক তথা দাঁতাল রাক্ষসের নিয়ন্ত্রণে। এই রাজনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হয় অসহায় মানুষ, আর লাভ হয় ধূর্তদের।
৫.
চেতনায় গভীরভাবে লালন করা দেশপ্রেমকে তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাস-কথকের স্ত্রীর নানার বাড়ি কলকাতার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত থানায়। সেই সূত্রে কথকের স্ত্রী ছোটবেলায় কলকাতায় যেতো। স্ত্রীর দাদা-নানির স্মৃতিচারণে উঠে আসে দেশবিভাগের কথা। ভারত-পাকিস্তান দেশভাগের ফলে তার নানির ভারতে থেকে যাওয়ার কথা আছে, আবার দুই দেশ এক হবে বলে দাদার বিশ্বাসের কথা আছে— যা অনেক বাঙালিরই মনের কথা। নানিকে স্ত্রী তুলনা করেছে হাসান আজিজুল হকের “আগুনপাখি” উপন্যাসের কথকরূপী মায়ের মতন, যিনি শেকড়ের টানে নিজের জন্মভূমিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের অসীম বাসনা পোষণ করেছেন :
স্ত্রী একটু সময় নিয়ে বলবে, বললো, আমার নানি হলেন কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের মায়ের মতোন; ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসে কথকরূপী মা যেমন বলেছিলো, চারাগাছ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না, তেমনি আমার নানিও এদেশের ভিন্ মাটিতে মরে যাওয়ার আশঙ্কায় তার বেড়ে ওঠার মাটি ছাড়েন নি, নিজ মাটিতে চলে গেছেন; কিন্তু, অন্য সন্তানদের ছেড়ে যাওয়ায় যে বুকে পাথর নিয়ে বেঁচে আছেন, তা আমি বুঝতে পারি। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৩৬)
সীমান্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে অসীম কৌতূহলে এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষকে অবলোকন করার কথা উঠে আসে লেখকের বর্ডারে পানি খাওয়ার ঘটনার স্মৃতিচারণে। তিন বিঘা করিডোর, আঙুরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহল প্রভৃতির কথাও উপন্যাসে আছে। রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তা ইত্যাদি গোলকধাঁধার বৃত্তে সীমান্তবর্তী মানুষের বেঁচে থাকার পাশাপাশি স্মৃতিচারণে প্রকটিত হয়ে উঠে রাষ্ট্রিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বৈরিতার চিত্র।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ঘটে কথকের সাথে তার দাদির কথোপকথনে। যেদিন দাদিদের নতুন কিংবা পুরান বাড়িতে মিলিটারিরা আগুন দিয়েছিলো, সেদিনের কথা উঠে আসে দাদির বর্ণনায় :
কাঁট্লের ঝুপির মতোন মোর গলাত্ একটা, কোলোত্ একটা, ঘাড়োত্ একটা, পিঠোত্ একটা, ফির দুই হাত দিয়্যা দুইটাক ধরচোং, ধরি দৌড় দৌড় দৌড়, পাও চলে না, তাও জান নিয়্যা এদিক ওদিক না দেখি ছিঁড়িছড়ি দৌড়াং দৌড়াং দৌড়াং; একজন মিলিটারি বাড়িত্ থাকা বাজোনোক সেদিন বন্দুকের নলা দিয়্যা ঘুতাইছিলো, কায়ো কায়ো কয়, বন্দুকের পাচা দিয়্যা খুউব জোরে ডাঙ্গাইছে, বাজোন কইছে, একজন মিলিটারি তাক একটা থাপ্রাইছিলো, আর একজন মিলিটারি তখোন বাধা দিছে, বাধা দিয়্যা ঐ বদমাইশ মিলিটারিটাক থামাইছে, কইছে, বুড্ঢোলোক, আঃ বুড্ঢোলোক; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৬৫)
দাদির বাপকে বুড়োলোক বলে মিলিটারিদের করুণা করে ছেড়ে দেবার ঘটনার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়ানো, মুক্তিযুদ্ধে মিলিটারিদের অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারা, কিংবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্য না হতে পেরে কথকের আক্ষেপ, আলুচাষী দাদুর মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা করার পরও প্রাপ্য সম্মান না পাওয়ার দিক প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক নানা বিষয় প্রকটিত হয়েছে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে। কথকের পিতাকে যুদ্ধে না যেতে দেওয়ার প্রশ্নে দাদি বলে :
ছাওয়ামানুষ কীসের যুদ্ধোত্ যায়, যার বাপ নাই, যার নানা মরি গ্যালো, যার ছোট ছোট ভাই-বইন আছে, যার মাও এ্যাকলায় কুকুর, বিলাই, শিয়াল, কাউয়া, চিল, বাদুর, ইন্দুর তাড়ায়্যা উক্যাস্ পায় না, তায় আবার কীসের যুদ্ধোত্ যায়, বাঁচি থাকায় তো যুদ্ধ! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৬৬)
মূলত অন্তবিহীন পথচলাই জীবন। আর এ পথচলায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাধীনতার গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যাই। পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। দেশবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথকের আক্ষেপকালে কথকের স্ত্রী যখন বলে দেশভাগ হলো বলেই বাংলাদেশ হলো, তারা প্রথম শ্রেণির চাকরি করে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে; তখন এ কথার প্রেক্ষিতে কথকের কথায় ফুটে উঠে সুগভীর জীবনদর্শন : “সর্বাত্মক মুক্তি কখনো আসে না; শুধু এক নদী থেকে উঠে আর এক নদীতে এবং এক জাল থেকে বেরিয়ে আর এক জালে পড়াই জীবন, জীবনের ইতিবৃত্ত; মুক্তি কিংবা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই জীবনে উপভোগ্য!” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৪০)
৬.
করোনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি তথা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, রাজনীতির উচ্চপদস্থদের ফায়দা লুটা, করোনাকে কেন্দ্র করে টিসিবির চাল-তেল চুরির ঘটনা, দুর্নীতি, কল-কারখানা বন্ধ হওয়ায় কর্মী ছাটাই, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর বেহাল দশা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, সরকারের অক্ষমতা ও নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতার কারণে জনসাধারণের সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুর্গতির চিত্র তথা জীবন ও জীবিকার আর্তনাদের আবেগী রূপ মূর্ত হয়েছে “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” উপন্যাসটিতে। যেকোনো দেশের মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির চাকা অচল হলে জনজীবনেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মানুষের মানসিকতাও ঠিক থাকে না; হতাশা, অবসাদ, কলহ লেগেই থাকে, বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে :
শরীরের একটি অংশে সুচ কিংবা হুল ফুটলে যেমন সারা অঙ্গ অবশ বা নিস্তেজ হয়ে যায়, তেমনি অর্থনীতির একটি সেক্টর কিংবা পরিবারের আয়ের একটি উৎস বিকল বা বাধাগ্রস্ত হলে হলে পুরো জীবনচক্র ও জীবনপদ্ধতিই আছড়ে পড়ে, টালমাটাল হয়ে যায়, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৯৬)
বিদেশী এনজিওতে চাকরি করতেন কথকের বাবা। সেই সুবাদে তার স্বপ্ন ছিলো সাহেব হবার। কিন্তু, একটা সময় পর তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন, বেসরকারি চাকারিতে টাকা বেশি হলেও জীবনের নিরাপত্তা নেই। দাদির জমি সব সন্তানদের মাঝে ভাগাভাগি করে দিয়ে ফেলার পর সব সন্তানদের কাছে তেমন দাম না পাওয়ার ঘটনায়ও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন নির্মম এক অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিক।
ঔপন্যাসিকের মতে, আমরা এমন এক সভ্যতায় উপনীত হয়েছি যেখানে রাজনীতি ও অর্থনীতির বেড়াজালে মানুষ হয়ে পড়েছে অসহায়; যেখানে আত্মগঠন, আত্মউন্নয়ন, আত্মবিকাশের চেয়ে রব উঠে আধুনিকতার। যেখানে লোকে প্রশংসা করে বাঘ কিংবা সিংহের; কিন্তু, ভালোবাসে গাধাকে। মাথা খাটানোর চেয়ে গতর খাটা লোকই মুনিবের পছন্দের থাকে। উন্নত দেশ গড়বার লক্ষ্যে আমাদের সবই থাকলেও সমন্বিত ব্যগ্রতা নেই বলে ঔপন্যাসিক মনে করেছেন। আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্যের মানুষেরা দৈবে নির্ভরশীল। প্রতীচ্যের মানুষ যেখানে আত্মপ্রত্যয় ও উদ্যম নিয়ে ইচ্ছা পূরণের ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় খুঁজে বের করে, প্রাচ্যের মানুষেরা সেখানে হাত গুটিয়ে বসে থেকে, অলৌকিক উপায়ে জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে বেড়ায়, বলে ঔপন্যাসিক মনে করেন। তাই তিনি বলেছেন :
আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে, সম্ভবনাময়ী উর্বর ক্ষেত্র আছে, কিন্তু, দারিদ্র্যমুক্ত বর্তমান নেই! সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, সবকিছুতেই রাজনীতিকরণ আর বিভেদ সৃষ্টির মানসিকতা এবং জাতীয় ভিশন, মিশন, ইউনিটি ও কন্সিস্টেন্সি তৈরিতে নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতার কারণে আমাদের সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুর্গতি! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৫৪)
৭.
শিক্ষা নিয়ে ঔপন্যাসিকের সুদূরপ্রসারী ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তথা ঘাটতি, বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃপণতা, শিক্ষকতা পেশাকে অন্য দেশে অনেক মূল্য দিলেও এদেশে হেয় করে দেখার প্রসঙ্গ উন্মোচিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের কলমের স্পর্শে। শিক্ষা লোক দেখানোর জন্য নয়, লেখাপড়ার মাপকাঠিতে শিক্ষাকে মাপা যায় না। কেননা, স্বশিক্ষিত মানুষ মাত্রই সুশিক্ষিত। শিক্ষার জন্য জাদরেল শিক্ষক নয়, বরং নিবিড় অনুধ্যান, আগ্রহ ও উন্মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন বলে মনে করেছেন ঔপন্যাসিক। তিনি বলেছেন, আত্মবিকাশ তথা আত্মগঠনে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন দৃঢ় প্রত্যয় ও সাধনা। সৎ ও সুন্দর পন্থায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংরক্ষণ ও আত্মসম্প্রসারণের ক্ষমতাকেই জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেনে ঔপন্যাসিক। এমন অনেক সার্টিফিকেটধারী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষই আছেন, যারা মূল্যবোধহীন তথা মনুষ্যত্ববর্জিত হয়ে থাকেন। তাই ঔপন্যাসিকের অভিমত, যারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত তারা কখনো খারাপ হয় না। ভালোদের লিমিটেশন আছে, কিন্তু মন্দদের কোনো লিমিটেশন নেই। দুর্নীতিগ্রস্ত, অসৎ কিংবা খারাপরা সবসময় সংঘবদ্ধ থাকে; সৎ ও আর্দশবানরা কোনো সিন্ডিকেট না করে একা চলতে ভালোবাসে। একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থে নিয়মের বাঁধনে সব আটকে রাখে, আর সৃষ্টিশীলরা সব বাঁধন ছিঁড়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে। এভাবেই ভাঙা-গড়ার নিয়মে বৃত্তাকার চক্রে পৃথিবী এগিয়ে চলে। লেখকের দৃষ্টিতে, এই বৃত্তাকার জীবনচক্রে অগ্রগতি আসবেই, সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়ে মানুষও তাদের স্বপ্নকে ছুঁতে পারবে। তবে, এই অগ্রগতি যদি সামগ্রিক ও সামূহিক না হয়, এর সুফল যদি সকলের মাঝে সম্প্রসারিত না হয়, কিংবা এর আলোকরশ্মি যদি অন্যকে আলোকিত না করে—, তবে এ সাফল্যের কোনো মর্যাদা নেই। ঔপন্যাসিক তাই দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করার কথা বলেছেন। কেননা, তিনি মনে করেন, “দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় দেশ-কাল-সমাজ এগিয়ে চলে। […] একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বস্ত হওয়া গেলেও পূর্ণ ও সামূহিক মানুষ হওয়া অসম্ভব।” (মাওলা প্রিন্স, ২৬৩-২৬৪)
জীবনের অপূর্ণতাগুলোর মাঝেও পূর্ণতা থাকে; একইভাবে, পূর্ণের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে অবসাদ, গ্লানি, অবক্ষয়। অর্থাৎ, জীবন যখন যেখানে যেমন, তেমন করেই নিজেকে বিকশিত করতে পারলেই জীবনের অগ্রগতি সম্ভব। সমকালের বৃত্ত অতিক্রম করে সমগ্রটা দেখতে পারাই সামূহিক মানুষের বৈশিষ্ট্য। লেখক তাই নিজেকে দাবি করেছেন একজন শিক্ষাবান্ধব শিক্ষক হিসেবে, যিনি নিজে সামূহিক ও পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসেন : “আমি শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষক নই, আমি শিক্ষাবান্ধব শিক্ষক। শিক্ষা ও আইনবান্ধব একজন শিক্ষক।” (মাওলা প্রিন্স, ২৭৯) নিজে যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মকেও স্বপ্ন দেখাতে হয়। জীবন সম্পর্ক ধারণা দিতে হয়, একত্রে হাসি কান্না ঐক্যবদ্ধ হওয়া শেখাতে হয়। মিথ্যা থেকে নিজেকে দূরে রেখে জীবনে সত্যের পথ বেছে নেওয়ার এক অনিন্দ্য মহাশক্তি লেখক অর্জন করেছিলেন। জ্ঞানত ও ধর্মত তিনি মিথ্যা বলেন না কখনো। ক্লাস থ্রিতে পড়াকালে লেখকের ভাবনায় উঠে আসে মিথ্যাকে নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ম অনুভব :
আমরা কথায় কাঁকর মেশাই, আমাদের কথার মধ্যে কাঁকর ছাড়াও অবাঞ্চিত মরা চাল আরা ধান থাকে, যেগুলো সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, কোনো উপকারে আসে না, বরং ক্ষতি করে, জীবনে আর পারষ্পরিক সম্পর্কে জটিলতা বাড়ায়, আমরা অযথাই মিথ্যুক আর মিথ্যাবাদী হই, মিথ্যার চর্চা করি, ধর্মমতে স্রষ্টার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হই, গোনাহ্ কিংবা পাপ করি; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৪১)
প্রত্যেক কর্মই মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় তথা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, আমরা কিছু হলেই অন্যের উপর কিংবা স্রষ্ট্রার উপর দায় চাপাতে অভ্যস্ত, নিজেরা দায় নিতে চাই না। নিজের জীবনের দায়ভার যে নিজেকেই নিতে হয়, অন্য সবাই যে এ দায়িত্ব পালনে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র, তা উঠে আসে লেখকের কথায়। কাজের মধ্যে থেকে জীবনকে একটু একটু করে নির্মাণ করতে হয়। করোনায় গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়া বন্ধুর প্রতি কথকের উপদেশে প্রকটিত হয় সেই সুগভীর জীবনদর্শন :
আর, শোন, মাটি কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয়, হবে, বারবার চাকুরি বদল করা যাবে না, আবার, আয়-উপার্জন করে বাসায় গিয়ে বসে থাকাও চলবে না, সবসময়ই কাজের মধ্যে থাকতে হবে, কাজ যতো ছোট হোক, বেতন যতো কমই হোক, কাজ করতে করতে শিখতে শিখতে দক্ষতা ও আস্থা অর্জন করতে পারলে একসময় ভালো কিছু হবেই; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১২৯)
৮.
প্রণয়ের ক্ষেত্রে উপন্যাসে আমরা রাবীন্দ্রিক এক প্রেমের আভাস পাই কথকের সাথে তার স্ত্রীর কথোপকথনে। স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে, প্রেমের প্রথম ভ্যালেন্টাইনে প্রেমিকাকে নিয়ে না ঘুরে তার দেওয়া “গৃহদাহ” বইয়ে ডুবে থাকা, তারপর সন্ধ্যায় দেখা হলে অপেক্ষারত প্রেমিকার কান্নার কথা। ভালোবাসা যে লোক দেখানোর কিছু নয়, বরং দুটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানব-মানবীর আত্মার মিল, আতুমির গল্পে বিভোর হওয়া—; ঔপন্যাসিকের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :
আমরা কি আত্মনিবেদনে আমাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করি নি, সংরক্ষণ করে চলি নি, চলছি না; […] আমরা বলতে আমরা কখনো তো তুমি আর আমিকে বুঝি নি, বোঝাই নি, আমি আর তুমিতে সীমাবদ্ধ হয় নি; আমি ও তুমি তো আতুমি, আর, আমরা অর্থ তো আতুমির সঙ্গে আরো কিছু, আরো আরে কিছু, অনেককিছু! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৪৮)
ভালোবাসার যে শক্তি, তার আলোকছটায় নিজেদের উজ্জীবিত করে গড়ে তোলার এক স্থির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। যাকে পেয়েছে তাকে নিয়ে পরিতৃপ্ত কিনা জানতে চাইলে প্রেমিক-কথক বলেন, তিনি যা চান তা ভুল করে চান না, তার প্রাপ্তি তার অর্জন। জীবনের এপিগ্রাম ওঠে আসে তার কথায় :
মানুষ তো কখনো শতভাগ পরিতৃপ্ত হতে পারে না, পারবে না, অতৃপ্তি মানুষের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য, চারিত্র্য গুণ, অতৃপ্তি মানুষের উপর বর্ষিত ঈশ্বরের অভিশাপ ও আর্শীবাদ, অতৃপ্তির জন্যই মানুষ একদা স্বর্গ ছেড়েছে, আবার, অতৃপ্তির জন্যই মানুষ গতিশীল, সৃষ্টিক্ষম, সৃজনশীল। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২২৭)
এছাড়াও স্মৃতিচারণে উঠে আসে, ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালে কথকের জন্য এক স্কুলপড়ুয়া মেয়ের পাগলামির কথা। যেখানে সবার পারস্পরিক মেলবন্ধনে তৈরি সংসার বহু বর্ণে বর্ণিল, বহু ব্যঞ্জনায় যূথবদ্ধ, সেখানে অতীতের কোনো স্মৃতির বিষ ছিটানো সম্ভব না বলে ঔপন্যাসিক মনে করেন। তাঁর মতে, পরিণত ব্যক্তি যখন বর্তমানে ঠেকে যায়, বৈরী পরিবেশ ও বিরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমান থেকে বাঁচতে চায়, তখন সে অতীতচারী হয়ে উঠে। অতীত স্মৃতিচারণ তথা স্মৃতিকাতরতা মানবিক সত্তারই পরিচয়। তবে, ব্যক্তি অতীত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বর্তমান ও কর্তব্যকে যেন ভুলে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেন ঔপন্যাসিক।
৯.
উপন্যাস-কথক যে উত্তরবঙ্গের মানুষ, —তা উপন্যাসে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষার নিখুঁত প্রয়োগও আমরা পুরো উপন্যাসজুড়ে দেখি। উত্তরবঙ্গ মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল। মঙ্গায় অভাবের তাড়নায় একসময় মানুষ তাদের সন্তানদের পর্যন্ত বিক্রি করে দিতো। কথকের দাদারা ছিলো তিস্তা পাড়ের নদী ভাঙা মানুষ। লেখকের স্মৃতি জাগানিয়া গ্রামের বাড়ির বর্ণনায় উঠে আসে বিমোহিত করা গ্রামীণ দৃশ্যপট। ভৌগোলিক কারণে উত্তরবঙ্গ খরাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় খরার সাথে যুদ্ধ করতো এ অঞ্চলের মানুষ। ফসলের পরিচর্যার পেছনে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হতো। ফসল জন্মালেও অভাবের নানা কারণ ছিলো। উপন্যাসে বীজ সংরক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে : “যেইক্না আছলো, তাও ইন্দুর-ধরেয়া খায়্যা ফ্যালাইছে, দেশি ইন্দুর আর বিলাতি ইন্দুর মিলি সৌগ নষ্ট কইর্ছে;” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৯) এখানে দেশী ও বিলাতি ইন্দুর রূপকী অর্থে যেন দেশীয় ও বিদেশী শোষকদেরই প্রতিনিধিত্ব করে; যারা নানাভাবে জোর-জুলুম-কারসাজি করে আপামর জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বেড়ায়। সরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগে আঞ্চলিক বঞ্চনা কিংবা বৈষম্য প্রসঙ্গে উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের মানুষের বঞ্চনার প্রসঙ্গ এসেছে :
এবার আসা যাক সরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগে আঞ্চলিক বঞ্চনা কিংবা বৈষম্য প্রসঙ্গে; মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সর্বপ্রথম খানা আয়-ব্যয় জরিপ হয় ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট বা রেকর্ড অনুযায়ী, সেই অর্থবছরে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের শতকরা হার ছিলো ৮০%, ১৯৮১-১৯৮২ অর্থবছরে এই হার ৭১%, ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে সেই হার নেমে ৪৮%, ২০০০ সাথে দারিদ্র্যের হার ছিলো ৪৪.৩%, ২০০৫ সালে ৪০.৪%, ২০১০ সালে ৩১.৫%, ২০১৬ সালে ২৪.৩%, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২০.৫%; অর্থাৎ, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ক্রমশ কমে এসেছে, হ্রাস পেয়েছে, নিঃসন্দেহে ভালো ব্যাপার; কিন্তু, উত্তরাঞ্চলের দিকে তাকালে দেখবে, রংপুর বিভাগে ২০১৬ সালেও দারিদ্র্যের হার ছিলো বা হচ্ছে ৪৭.২% এবং দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপ্রবণ দশটি জেলার পাঁচটিই রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলা; অবশ্য ২০১০ সালে রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার ছিলো ৪২.৩%; তাহলে, কী দাঁড়ালো, নিশ্চয়ই সরকার এই অঞ্চলের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয় নি, কিংবা, কোনো কার্যকরী উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা, বঞ্চনা করেছে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলকে, পুরো উত্তরবঙ্গকে! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৯)
১০.
বাঙলা ও বাঙালি জনপদের পরিচয়, ইতিহাস, অনার্য-আর্যের ক্রমবিকাশ, মানুষের ক্রমবিকাশ, বাঙালির বিবর্তনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও পুরাণের আলোচনা, অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান বা এনথ্রোপলজি, অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষবিদ্যা, নব নব আবিষ্কারের কথা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রাচীন স্থাপত্যকলা ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, কাঞ্চনজঙ্ঘা, হিমালয় পর্বতমালা, তাজমহল, অজন্তা গুহা ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান, সিন্ধু সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথামালা প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাসে। এছাড়াও গুগোল ও উইকিপিডিয়ার সহায়তায় এবং স্মৃতিচারণে বিভিন্ন রাজা ও সাম্রাজ্যের কথা; তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, চিকলী, মরাসতী, করতোয়া, বুড়ি তিস্তা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নদীর নাম ও পরিচিতি উঠে আসে।
১১.
কোভিডের ভয়াবহতা মানুষের মনে শিহরণ জাগায়, তৈরি করে খোদাভীতি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ধর্মীয় নেতার মৃত্যুতে কঠোর লকডাউনেও তাই জানাজায় মানুষের ঢল নামে, মসজিদ কিংবা ধর্মীয় উপাসনালয় লকডাউনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বন্ধ করা হলেও মৃত্যুচিন্তায় অসচেতন মানুষজন জড়ো হয় উপাসনালয়ে। মসজিদে পানিভর্তি একই চৌবাচ্চা থেকে অসচেতন মানুষেরা ওযু করে। শৈশবের শিক্ষকের ছেলে, চিল্লার কথা বলে নিরুদ্দেশ হওয়া ভার্সিটিপড়ুয়া ছেলেকে খুঁজতে যাওয়া কথক নিজেও শামিল হয় তাদের সাথে। কেননা— “ধর্মের চেয়ে যে সমাজ বড়, শাস্ত্রবিধির চেয়ে সংস্কার।” WHO এবং UN করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুর্যোগের আশঙ্কা করছিলো, তা তরান্বিত করতেই যেন আগমন ঘটে ঘূর্ণিঝড় আমফানের। পৃথিবীর মানুষের যে বাড়াবাড়ি তা যেন এক কোভিডের আতঙ্কে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বিশ্বরাজনীতির ইঁদুর দৌড়ে উত্তপ্ত পৃথিবী কোভিডের থাবায় ক্ষণিকের জন্য হলেও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আমপানে বা আমফানে মানুষের দুর্ভোগের চিত্রও উপন্যাসে রূপায়িত হতে দেখি। ১৭ই মার্চের একদিন আগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, করোনাকালে কেউ মারা গেলে পুলিশের নানা বিধান, লকডাউনে পুলিশের লাঠিচার্জ, শ্রমজীবী দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের অসহায়ত্ব, করোনায় অন্যান্য মানুষের পাশাপাশি আশ্রয়ের প্রতীকরূপী ডাক্তারদের প্রাণহানী, করোনার টিকা আবিষ্কারের কথা, কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে সত্য-মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, পিপিআই ও মাস্ক কেলেঙ্কারির ঘটনাসহ করোনা নিয়ে বৈশ্বিক বিবিধ প্রসঙ্গের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। করোনায় প্রতিদিনই নতুন নতুন এসব সংশয় ও উৎকণ্ঠার মাঝেও লেখকের প্রত্যাশা, করোনা দ্রুত পৃথিবী ছাড়বে এবং সাথে করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর সব মন্দ দিক :
যদি এখন কেউ আমাকে বলতো, করোনাবাহিনী চলে যাওয়ার সময়ে তাদের থলেতে, তাদের সুটকেসে, তাদের পকেটে, তাদের বাহনের খোলে পুরে দেয়া হবে পৃথিবীর যতো পাপ-তাপ-কালিমা-অনাচার, সমাজের যতো জারিজুরি, রাষ্ট্রের যতো জোড়াতালি, জীবনের যতো জোচ্চুরি; যদি কেউ বলতো, […] আসন্ন সূর্যোদয় থেকে শুরু হতে চলেছে সভ্যতার নতুন পথচলা, ঐ দেখো ঐ আলোর রেখা, ঐ শোনো বাজলো ঐ সুহৃদ-ঘণ্টা, ঐ দেখো ঐ প্রাঞ্জল-ফোয়ারা, ঐ শোনো বাজছে ঐ সুপ্রাণ-মনটা! সুহৃদে প্রাঞ্জলে সুপ্রাণে সতেজ পৃথিবী পৃথিবীর আলোকবর্ষা, আয়োজন-ঘনঘটা! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৩১)
করোনায় কথকরূপী ঔপন্যাসিকের মাথার ভেতরে বেজে চলে মৃত্যুর এক নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি— “বিশ আর বিশ দুই হাজার বিশ, না-কি বিষ আর বিষ, সালটা ২০২০।” এই ক্রান্তিকালে ঘুরেফিরে মৃত্যুর চিন্তাই ভর করে কথকসহ সবাইকে। জ্বরে, ব্যথায় অসুস্থ তথা কাবু হওয়া কথকের চিন্তায় আতঙ্কগ্রস্ত স্ত্রীও যখন একসময় বলেন যে, তিনিও ঘ্রাণ পাচ্ছেন না; তখন ঘোরে থাকেন কথক। কথকের চৈতন্যে ফুটে উঠে ভয় ও সাহস, স্বস্তি ও যন্ত্রণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনার এক চক্রাকার বৃত্ত। চরম অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকা কথক বুঝতে পারেন না তিনি ঘুমাচ্ছেন নাকি জেগে আছেন। এভাবেই শেষ হয় “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” উপন্যাসের।
১২.
জীবনে চলার পথে অচেনা পথ পাড়ি দিতেই হয়, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, কোথায় থাকবো কেউ জানি না। অনিশ্চিত এ জীবন, কিন্তু থিতু হতে চাইলেও আমরা স্থির থাকতে পারি না। জীবনের তাগিদে, বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের এই অনিশ্চিত পথ পাড়ি দিতেই হয়, —এটাই জীবন। ঔপন্যাসিকের মতে, আমরা সবাই জিপসি ম্যান—, এই অনিশ্চিত পথ থেকেই আমাদের খুঁজতে হবে আমাদের বিশ্বাসের হাড়-মূল।
করোনাকে ঔপন্যাসিক তুলনা করেছেন একটা বিশ্বযুদ্ধের সাথে, যে যুদ্ধে নিরাপদ থাকাই প্রথম কথা। পৃথিবীতে এ যাবতকালে প্লেগ, কলেরা, যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন মহামারীতে বহু মানুষই মারা গেছে। কিন্তু, সেসবের ঔষুধও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, করোনারও হবে বলে ঔপন্যাসিক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের নামকরণে তাই সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার শাশ্বত ইচ্ছাকেই লেখক প্রকটিত করেছেন : “মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে এবং যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকবে। […] জীবন হারতে হারতেও জিতে যায়। জীবন জিততে জিততেও হেরে যায়। কিন্তু, জীবন নিঃশেষ হয়ে যায় না।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৫০) পলিসির যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ফসল উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অসহায় আলুচাষী দাদুর কথায়ও আমরা উপন্যাসের নামকরণের দিকটি প্রকটিত হতে দেখি। আলু্চাষী দাদু বলেন : “কী আর করবু, এইটাই জীবন, এইটাই জীবনের চক্র, এইভাবেই মাইনষে যুদ্ধ করি বাঁচি থাকে, যুদ্ধ কইরবার না পারলু ত্যা মরার আগোত্ মরলু।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৫৮) পৃথিবীতে টিকে থাকার লড়াইয়ে এবং শান্তি ছিনিয়ে আনতে আমরা সবাই এক একজন অভিনেতার ভূমিকা পালন করে চলেছি— “অ্যাক্টিং ইজ আর্ট অফ লাইভ, ইটস হ্যাভ ওয়ার্ল্ড ডিমান্ড ইন ওয়ার এন্ড পিস।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৭১) উপন্যাসের বর্ণনায় আমরা দেখি, কথক তথা ঔপন্যাসিক তার ছেলেবেলায় কবুতর পালতেন। শান্তির প্রতীকরূপী এই কবুতর প্রতিপালনের প্রসঙ্গ উপন্যাসের নামকরণকে যেন আরো জারালো করে তুলে। এছাড়াও ঔপন্যাসিকের ভাবনা-চিন্তায় এবং কাহিনির বিস্তৃত পরিসরে বারবার আমরা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতার দিকটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি :
আন্দোলনই জীবন। জীবনকে বৃহৎ-পরিব্যাপ্ত কিংবা ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করলে আন্দোলনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। যেতে পারে। আন্দোলন এক অর্থে কম্পন। অনুক্ষণের শ্বাস-প্রশ্বাস। আর-এক অর্থে আলোড়ন। প্রাত্যহিকের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম। বোধকরি দুটোই হচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াই। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রতিক্ষণ লড়াই করে; এবং লড়াই করেই তাকে বাঁচতে হয়। ( মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ২৬২)
মানুষ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধ কখনো শেষ হয় না। এক যুদ্ধ শেষ হলে আরেক যুদ্ধ শুরু হয়। এভাবেই বেঁচে থাকার যুদ্ধ চালিয়ে যায় মানুষ। এই যুদ্ধ ব্যক্তিক জীবন থেকে সামষ্টিক জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়, গণআন্দোলনে রূপ নেয়। যুদ্ধ এবং শান্তি— নামকরণে তাই ঔপন্যাসিক মানুষের বেঁচে থাকার এই শাশ্বত দ্বন্দ্ব-সংগ্রামকেই ধ্বনি-তরঙ্গময় করে উপস্থাপন করেছেন।
১৩.
“বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্সের এক গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী উপন্যাস। ঔপন্যাসিক এখানে ক্রান্তিকালকে সামনে রেখে বিরতিহীন ও শ্বাসরুদ্ধকর আখ্যান দিয়ে নিপুণভাবে সমগ্র মানবজীবনকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ঔপন্যাসিকের কলমের জাদুকরী স্পর্শে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পুরো উপন্যাসজুড়ে কোথাও কোনো চরিত্রের নাম ব্যবহার না করেও সম্বোধনবাচক শব্দে অসাধারণ পারঙ্গময়তায় পুরো আখ্যান রচনা করে গেছেন তিনি। তবে, চরিত্রের সম্বোধন কিংবা ক্রিয়ার ব্যবহারের যে শব্দের খেলা তিনি খেলেছেন, তাতে ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হলেও মাঝে মাঝে পাঠকের নিবিড় পাঠে ছেদ ঘটাতে পারে। উপন্যাসে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির কথা যেমন আছে, তেমনিভাবে আছে সমগ্র বিশ্বকে চিত্রায়ণের একনিষ্ঠ প্রত্যয়। ব্যক্তি, দেশ, কাল, রাষ্ট্র, বিশ্ব, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রেম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাভাবনা, ক্রান্তিকাল, হতাশা, ব্যর্থতা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যয়, আশাবাদ, মৃত্যচিন্তা— সমগ্রকে ধারণ করার এমন স্থির প্রত্যয় খুব কম সাহিত্যকর্মেই আছে। এদিক থেকে উপন্যাসটি সার্থকতার দাবিদার। শৈল্পিক বিচারেও ঔপন্যাসিক তাঁর স্বাতন্ত্র্যিকতার জায়গা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর। সার্বিক বিচারে, “বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি” মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের তথা জীবনের গতিপথের এক অনবদ্য আখ্যান। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যে দূরদর্শিতা ও গভীর জীবনদর্শনকে ভাব-ভঙ্গিমায় রূপায়িত করেছেন, তা কালের বিচারে অক্ষয় হবে।


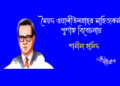








Discussion about this post