সৈয়দা কামরুন্নাহার লিপি
উপন্যাস বা নভেল হচ্ছে এক ধরনের কল্পকাহিনির লিখিত রূপ। সাহিত্য-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীর মতে, “উপন্যাস একটা জীবনের অখণ্ড রূপায়ণ এবং সমগ্রতাই তার মর্মবস্তু। একটি অর্থপূর্ণ অতীতের উৎস হতে উদ্ভূত হয়ে যে জীবন দূর ভবিষ্যতে বিসর্জিত আর বর্তমান তার সাম্প্রতিক স্থিতিকাল।” সাহিত্য-সমালোচক সুবোধ সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বলেন, “সচেতন ও অর্ধচেতন আত্মার উপরে বাহিরের ঘটনার আঘাত করিলে যে সকল নিগূঢ় অনুভূতি জাগে, তাহার অভিব্যক্তিই উপন্যাস।” ব্যুৎপত্তিগত এবং আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, মানব-মানবীর জীবন-যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষ বিন্যাসসহ গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়, তাই উপন্যাস। যেহেতু উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবন তাই উপন্যাসের কাহিনি হয় বিশ্লেষণাত্মক, দীর্ঘ ও সমগ্রতাসন্ধানী৷ (দ্র. গৌরব রায়, ২০২৩)
মাওলা প্রিন্স একজন কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও গবেষক। পেশায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। তার প্রকাশিত উপন্যাস বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি (২০২২) অবলম্বনে সামান্য পাঠপ্রতিক্রিয়া উপস্থাপনের প্রয়াস এ রচনা। এটা একটা সামাজিক উপন্যাস। একটি দরিদ্র পরিবারের মানুষ কীভাবে নিজেদেরকে তিলে তিলে গড়ে তুলে সামাজিক অবস্থান তৈরি করতে পারে, যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারে, জীবন যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত আলোচনা হয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজের চোখে তার আশপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক পারিপার্শ্বিকতা অবলোকন করেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তুলে এনেছেন অবহেলিত জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার যুদ্ধ বা লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত।
মানুষ মরণশীল। তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। তবুও মানুষেরা যুদ্ধ করে বাঁচতে চায়, দুনিয়ায় আরও কিছুকাল লড়তে চায়। ঔপন্যাসিক করোনাকালের ভয়াবহ অবস্থা, জ্যান্ত মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসহায় মৃত্যুর মহামিছিল, মানুষের এক নিয়মে ঘরবন্দি, এক ভাবনায় আচ্ছন্ন, এক শঙ্কায় শঙ্কিত, এক আতঙ্কে আতঙ্কিত নির্ঘুম সময়ের করুণ আখ্যান দিয়ে শুরু করেছেন হাঁটা। কোভিট-১৯ মানুষকে কীভাবে নতুন করে ভাববার শিক্ষা দিয়েছে তা তুলে এনেছেন, বর্ণনা টেনেছেন মুক্তিযুদ্ধেরও। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলা, ভয়, হতাশা, অসহায়ত্ব, সনদ কেনাবেচা, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, সন্তানদের চাকরি-বাকরি গ্রহণ, ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দৌরাত্ম্য নিয়েও আক্ষেপ উঠে এসেছে। পারিবারিক জীবনের একান্ত টুকরো টুকরো ঘটনার জটলা তুলে এনেছেন নিখুঁতভাবে। নানার বিয়ে, মা-বাবার পারিবারিক মেলবন্ধন, বড় নানীর সতীনের সংসার, কান্না আহাজারি সবকিছুই এসেছে বর্ণনায়।
করোনাকালীন ভয়াবহ চিত্র, সরকারের প্যাকেজ প্রণোদনা, গার্মেন্টস মালিকদের খুশি আনন্দ, শ্রমিকদের আহাজারি, হাটবাজারের করুণ আখ্যান, লকডাউন মানা না মানা, ভোটের রাজনীতি কী না বলেছেন তিনি। করোনা মোকাবেলায় সরকারের হিমশিম খাওয়া, যথেষ্ট মাস্ক, পিপিই ও অক্সিজেন না থাকা, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্কট, সরকারি চিকিৎসকের করোনা সেবা দেয়ার অনীহা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ায় ডাক্তার, কবিরাজ, এমনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যু ও অসহায়ত্ব—, এসব দৃশ্যের বর্ণনা এসেছে এভাবেই :
এখনো বেঁচে আছি, আক্রান্ত হই নি, দেশ এখনো ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে শতগুণ ভালো আছে, এতেই আলহামদুলিল্লাহ। নিশ্চয়ই মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। হঠাৎ মারা যাওয়ার চেয়ে হাঁচি-কাশি, জ্বর মাথাব্যথায় একটু একটু করে মারা যাওয়াই তো শ্রেয়! না গো ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয় করোনায়। (২০২২ : ১৯)
কী নিদারুণ আক্ষেপ, অনুনয়, আবেগ আকুলতা! অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনকাহিনী ফুটে উঠেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনমান, ঈদে নতুন জামা না পাওয়ার হাহাকার, স্বল্প বেতনের সংসার পরিচালনার করুণ আর্তির দৃশ্যায়ন নতুন করে ভাবনার সৃষ্টি করে। লেখকের ভাষায় :
যখন আমরা গ্রামের বাড়িতে ছিলাম, অষ্টআশি সালের বন্যার সময় কিংবা আগে পরে কোনো এক সময়ে হবে, একদিন বাড়িতে ভাত রান্না হয় নি, ভাত কেনো, গম, আটা, কাউন, আলু, মুড়ি, কাঁঠাল কিছুই ছিলো না ঘরে, শুধু ঘর বা বাড়িভর্তি মানুষ ছিলো, এক পাল ক্ষুধার্ত মানুষ, নিরুপায় মানুষ, নিশ্চুপ নিরুৎবিগ্ন সব ভদ্র জোয়ান মানুষ; শিশু আমি ভাত ভাত করে কাতরাচ্ছি কিংবা লালাচ্ছি অথবা ঘ্যানঘ্যান করছি আম্মুর আঁচল ধরে, তখন আম্মু আব্বুকে দেখিয়ে দেয়, আব্বু বলে তোমার দিদিকে গিয়ে বলো, দিদি বা দাদিকে বললে দাদি বা দিদি বললো, মোর গোস্ত খা! (২০২২ : ২১)
আমরা উত্তরাঞ্চলের মানুষ। বারবারই ঠকেছি আমরা। ১৯৭৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপ্রবণ দশটি জেলার পাঁচটিই রংপুর বিভাগের। সরকার এই অঞ্চলের জন্য যে কার্যকরী কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেয় নি, তা নিশ্চিত। আমরা বারবারই বঞ্চিত হয়েছি, বঞ্চনার স্বীকার হয়েছি। দীর্ঘদিন সেনাপ্রধান ও একনায়ক শাসক এরশাদ (১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ০৬ ডিসেম্বর ১৯৯০) পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিন্তু রংপুরের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করেন নি তিনি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বগুড়ার সন্তান, তার স্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম ও জন্মোত্তর শৈশব-কৈশোর কেটেছে দিনাজপুরে। এদিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুরের পুত্রবধূ। তবুও আমাদের উন্নয়ন হয় নি বলে আক্ষেপ টেনেছেন ঔপন্যাসিক।
এ উপন্যাসে নানা-নাতির অসাধারণ গল্পের উপাখ্যান বেশ রোমাঞ্চকর। নাতি মায়ের থেকে নানার দুই বিয়ের কারণ জানতে চাইলে, মা বলেন :
মার সঙ্গে এ্যালা কীভাবে বিয়া হইলো বলতে পারি না; আর, কবোইবা কীভাবে, আমাদের মা ছিলো পাগলি, বোবা, ঠিকমতো মন খুলি কোনোদিন মার সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই; আব্বা খুব রাগি হওয়ায়, আর আব্বার ট্রাঙ্কের ভেতরে বাঁশের চ্যাবারি আর কঞ্চি থাকায়, আমরা আব্বার কাছ থেকে পালায় পালায় বেড়াতাম, সৎমায়ের কাছে থেকে বড় হইছি, তার সাথেও ভালো করি কতা বলা গ্যাছলো না; (২০২২ : ৯৮)
গল্পে উল্লেখ আছে, বড় নানির বাবার আম্মু বা মায়ের, অর্থাৎ বড় নানির দাদির খামখেয়ালির কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন নানা। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :
আমাদের নানাজির আম্মু বা মা বা মায়ো বা মাজান বেড়াবার আসে, ব্যাড়াবার আইসসে; তায় আসি আব্বার রাগ দ্যাখে, চিল্লাচিল্লি শোনে; তখন আমাদের মাজা তার নাতিজামাইয়ের সাতে মজাক করি নাকি হাতে তালি দিয়্যা বইলছে, বোলছিলো, হামরায় দেখি তোকে মেয়ে দিছি, আর কায়ো তোক মেয়ে দিবে, তোর মতো বাউদিয়াক কায়ব্যা বেটি দ্যায়! (২০২২ : ৯৮)
এরপর নানা জেদি হয়ে ওঠে, পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বড় নানির কপালে সতিন জোটে। বড় নানি তার বাপের বাড়ি চলে যায়। সেখানেই সন্তানদের লালন-পালন করে মানুষ করে গড়ে তোলেন।
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর অবস্থিত। ভারতের নিয়ন্ত্রণে যা স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখণ্ড আঙুরপোতা-দহগ্রামের প্রবেশমুখ। উপন্যাসে কাঁটা-কাঁকড়-কাঁটাতার বেষ্টিত এখানকার করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে এভাবে :
ও এক বিচিত্র স্থান, না গেলে বোঝানো কঠিন, আঙুরপোতা-দহগ্রাম বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, আর, দ্বীপের চারিদিকে দৈত্যরাজ সমুদ্রবেশী ভারত; নদী কিংবা সমুদ্র পার হয়ে দূরবর্তী সেন্টমার্টিন যাওয়া যায়, কিন্তু জলজ কাঁটা-কাঁকড়ে পূর্ণ সমুদ্ররূপী ভারত অতিক্রম করে সন্নিকটবর্তী আঙুরপোতা-দহগ্রামে প্রবেশ করা কঠিন। (২০২২ : ১৪২)
বেড়াতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন কথকরূপী ঔপন্যাসিক। তিনবিঘা করিডোরে পিকনিকে আসা ভারতের সেই আয়োজনে এক সুন্দরী, হৈমন্তীর মতো যার দেহের গড়ন, বাড়ন্ত চেহারা, ফর্সা মেয়ের দেখা পান তিনি। সে যেন তাকে দেখছে। কথকও কৌতূহল হয়ে তাকে দেখছেন। এক অজানা মায়ায় পড়ে যান তিনি, হয়তো মেয়েটিও। শুরু হয় হৃদয়ের প্রেম-প্রণয়। সৃষ্টি হয় স্পর্শের আকুলতা। আবার, হারিয়ে যান অজানা আতঙ্কে। হৃদয়ে শিহরণ জাগে। কষ্ট-নদী সাঁতরাতে থাকে। হৃদয়-মনে বিড়বিড় করে উচ্চারিত হয় :
সীমান্ত এলাকায় কী এক কৌতূহল ও অবাধ্যতার স্পৃহা নিয়ে যে এক দেশের মানুষ অচেনা অজানা আর এক দেশের মানুষকে অবলোকন ও আকাঙ্খা করে, তারা কীভাবে যে তাদের সুতীব্র হৃদয়াবেগকে সংযত ও সংবরণ করে রাখে, ওখানকার স্থানীয় মানুষগুলো দেশ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তা ইত্যাদি গোলকধাঁধার বৃত্তে যে কীভাবে বেঁচে থাকে, তা বোঝানো অসম্ভব; (২০২২ : ১৪২)
করিডোর সীমাবদ্ধতার এই করুণ আর্তি মানবতার বিরুদ্ধে বিষবাষ্প যেন। লেখক চোখে আঙুল দিয়ে তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।
ঔপন্যাসিক ক্ষণে ক্ষণে বাঁকবদল করেছেন, মানবতার ফেরিওয়ালাদের বুঝাতে গিয়ে অসাধারণ কিছু প্রেক্ষাপটের অবতারণা করেছেন। কবুতর শান্তির প্রতীক। শখের বসে আনন্দের আহ্লাদে মানুষেরা কবুতরের লালন পালন করেন, কবুতরের চাষ করেন। কবুতরের সাথে আনন্দ করেন, তার বাড়ন্ত বয়সের সাথে প্রজন্ম পরম্পরায় উন্নতি কামনা করেন। সেজন্য প্রয়োজন মতে কেনাবেচাও করেন। তবে একটা আকুতি, একটা হাহাকার থেকেই যায়। এই লালন-পালনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য দিকের সাথে মেলবন্ধন তৈরির ছক এঁকে দিয়েছেন তিনি। ট্রাকের সাথে সাইকেল দুর্ঘটনার ঘটনাপ্রবাহ তৈরি করে মানব জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর উপমা টানতে চেয়েছেন হয়তো। ঔপন্যাসিকের ভাষায় : ‘স্কুলে গিয়েও আমি ওদের কথা ভাবতাম, সুযোগ পেলেই বন্ধুদের শোনাতাম আমার প্রিয় শখের কথা, আমার প্রিয় কবুতরগুলোর কথা, শান্তির দূত একঝাঁক পায়রার কথা।’ (২০২২ : ১৭৩)
লেখক আলোচনার পরতে পরতে নানাবিধ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো তুলে এনেছেন। এঁকেছেন নতুন নতুন চিন্তার জগৎ। আমাদের সবাইকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যেতে হবে। তার কাছেই সকল বিপদ মুসিবতে সাহায্য চাইতে হবে। মানুষেরা, বিজ্ঞানীরা, ডাক্তারেরা অনেকেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না। তাকে মানতে চায় না। লেখক করোনা অনুজীবের সাথে মানুষের পেরে উঠতে না পারায় টাইটানিক জাহাজের করুণ পরিণতির উদাহরণ টেনে আমাদের সতর্ক করেছেন। তিনি লেখেন :
দেখো, ঔষধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গত এক-দেড় দশক থেকে বলতে শুরু করেছিলো যে, মানুষের মৃত্যুকে তারা জয় করবে, অন্তত মানুষকে একশো-দেড়শো বছর বাঁচিয়ে রাখবে; আর, এখন সামান্য একটা অণুজীবের পেছনে সারা বিশ্ব একসঙ্গে ছুটছে, গবেষণা করে অনুজীবটির চরিত্র-চারিত্র্য গতি-প্রকৃতি সক্ষমতা-সীমাবদ্ধতা ধরতে চাইছে, অথচ, কিছুই করতে পারছে না, সামান্য জ্বর কাশি ব্যথা শ্বাসকষ্টেই এখন বিজ্ঞানীরা কাবু! টাইটানিক জাহাজের করুণ পরিণতির মতো; টাইটানিকের ক্যাপ্টেন-ক্রু-কর্তৃপক্ষরা নাকি বলেছিলো এ জাহাজ আইসবার্গ কেনো স্বয়ং ঈশ্বরও ডোবাতে পারবে না; অথচ, আটলান্টিক সাগরের বুকে পাঁচ দিনও টিকতে পারলো না, আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা লাগার মাত্র চার ঘন্টার মধ্যেই সব শেষ, নিমিষেই ডুবে গেলো পনেরো হাজার মানুষ! (২০২২ : ১৭৮)
আমাদেরকে সচেতন করতে, সজাগ হতে, মনোজগতের পরিবর্তন আনতে ঔপন্যাসিকের কত চেষ্টা, প্রচেষ্টা। এভাবেই লেখক এগিয়ে গেছেন বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন চিন্তা-চেতনায়।
মানবিক ভালোবাসা, হৃদয়ের আকুতি ও আকুলতা, পারস্পরিক আকর্ষণ টান—, এ যেন স্বপ্ন-সারথি। যূথবদ্ধ জীবন পরিচালনার দায়বদ্ধতা। প্রেয়সী কিংবা স্ত্রী একে অপরের কাছে আসবার টান তুলে এনেছেন নিখুঁতভাবে। যেমন :
প্রেয়সী-স্ত্রী হয়তো কাছে আসবার নিমিত্তে বলে, বলবে, তোমার মাথার চুলগুলো একটু টেনে দিবো, হাত-পা টিপে দিবো, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই তোমার কোমর ধরে গেছে, দাও একটু ম্যাসেজ করে দি, আরাম পাবে। না থাক, একটি ভদ্রমহিলা, যে কিনা আমার প্রেয়সী, তাকে দিয়ে পা মর্দন করা অশোভনীয়, আমার বিবেকে বাধে। (২০২২ : ২৩০)
এভাবেই এগিয়ে যান ঔপন্যাসিক তার অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। মুক্তির মোহনায় ফিরে আসেন ঔপন্যাসিক। প্রেয়সীকে খুশি করতে গিয়ে তিনি যে মিথ্যা বলেন না কখোনোই, তা উঠে এসেছে লেখকের ভাষায় :
কেনো মিথ্যা বলবো, কী জন্য কিংবা কিসের জন্য কিংবা কার জন্য মিথ্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াবো; হোক না তা হিজিবিজি মিথ্যে, কাতুকুতু মিথ্যে, বিন্দুবিসর্গ মিথ্যে, নির্দোষপ্রায় গুড়চিনি মিথ্যে; মিথ্যার সঙ্গে আড়ি, জনম জনমের আড়ি, মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যে আমার বৈরী; এবং একসময় উপলব্ধি করলাম যে, আমি সত্যের শালদুয়ারে দাঁড়িয়ে একটা শক্তি পাচ্ছি, মানুষ যাকে অলৌকিক শক্তি বলে, হয়তো তাই, হয়তো তার মতো অন্যকোনো অনিন্দ্য মহাশক্তি, হয়তো তার কাছাকাছি অন্যকোনো অসীম ক্ষমতা, অথবা, কোনো পরম সামর্থ্য; যা আমি ভেতরে-বাহিরে টের পাই, অনুভব করি! (২০২৩ : ২৪২-২৪৩)
এই সত্যিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে ফিরে আসেন স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঠে, ময়দানে, যোদ্ধাদের সংস্পর্শে। তাদের আকুতি ও আকুলতা শোনেন, বোঝেন এবং দেশকে নিয়ে ভাবেন। একসময় মুক্তিযুদ্ধের নানাবিধ প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে দাদুর কাছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয় জানতে চাইলে রাগত স্বরে দাদু বলেন :
দাদু, আপনি নাকি যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু, আপনার সার্টিফিকেট নেই? তখন দাদু বুক চেপে ধরেন এবং অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠেন এবং গর্জে উঠে বলতে থাকেন, মুক্তিযুদ্ধের কথা মোর সামনে কোনোদিন কইস না, এই কথা তুললে বুকটা ফাটি যায়, তখন আমার মধ্যে আমার ভিতরাত কী যে উথাল-পাতাল শুরু হয়্যা যায়, আমি ঠিক থাইকবার পারি না, খালি চিৎকার দিয়া কান্দন আইসে। (২০২২ : ২৫৮)
একজন মুক্তিযোদ্ধার এই আকুতি ও আকুলতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। আমাদের হতাশ করে। এজন্যই হয়তো লেখক আফসোস করে আরেক জায়গায় লিখেছেন :
সবাই ছুটছে, ছোটাছুটি করছে, ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে যেতে চাইছে। যেভাবেই হোক তাকে সামনে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। এগুতেই হবে। শুধু এগুলেই হবে না, বাহবা অর্জন করতে হবে, শুধু বাহবা ও হাততালি নয়, রায়বাহাদুর অথবা বীরবাহাদুর অন্তত কোন একটি খেতাব অর্জন করতেই হবে, আধুনিক সমরসজ্জিত কমরেড কিংবা কর্নেল হতেই হবে এবং সেজন্য তাকে সবুজ শৈশব সহজ খেলনা ছেড়ে দৌড়াতে হবে, কৈশোরের কমলা রোদগুলোকে আড়ি দিতে হবে, বন্ধুত্বকে অস্বীকার করতে হবে, ভুলে যেতে হবে লাটাই-ঘুড়ি, রঙিন কাগজ, কাগজের নৌকা, বাঁশের বাঁশি, কাঁঠাল ও কাগজি লেবুর ঘ্রাণ। (২০২২ : ২৭০)
কী নিদারুণ আক্ষেপ! কী অন্তরজ্বলা! আহা! আমরা স্বাধীন নাকি বিবেকের তাড়নায় পরাধীন। ঔপন্যাসিক তার চিন্তার বিস্তৃতি কতদূর নিয়ে গেছেন!
এভাবেই ভাবতে ভাবতে সময়ের ব্যবধানে ঔপন্যাসিক আবারও ফিরে আসেন করোনা পরিস্থিতির সম্মুখপানে। এতো কিছু হচ্ছে, করোনা কীভাবে সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, তবুও আমরা সচেতন হচ্ছি না। দায়িত্ব পালনে সৎ ও মহৎপ্রাণ হচ্ছি না। একসময় ভাবতে গিয়ে ফিরে আসেন দাদির করোনা বিলাপ নিয়ে, দাদার আকুতি ও আকুলতা নিয়ে, নিজের প্রেয়সী-স্ত্রী করোনা পজিটিভ হলে কী ভয়ানক পরিস্থিতি হতে পারে, তা নিয়ে। এসব ভাবনার এলোমেলো নিয়েই সমাপ্তির পট তৈরি হয় উপন্যাসের। মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র এঁকে দিয়েছেন পাঠকের হৃদয়ে। নিজেদের পরিবারের মানুষজন নিয়ে ভেবেছেন। কবর এবং কবরস্থান সংস্কার নিয়ে ভেবে ভেবে সবাইকে কবরের প্রস্তুতি নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রতীকাশ্রয়ে। অসাধারণ উপন্যাসটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনায় সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল মনোভাব তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সবমিলিয়ে চমৎকার উপন্যাসটির জন্য লেখক সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবুও দুটি কথা না বললেই নয়; লেখায় কিছুটা একরোখা মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, অধ্যায় ভিত্তিক বর্ণনা না আসায় কখনো বোরিং লেগেছে। একই শব্দ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক আরেকটু সচেতন হলে এগুলো এড়িয়ে যেতে পারতেন। আবার, অন্যভাবে বললে এগুলোই হয়তো ভাষা ও শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এগুলোতেই নিহিত রয়েছে ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র। ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্সের অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কামনা করছি।

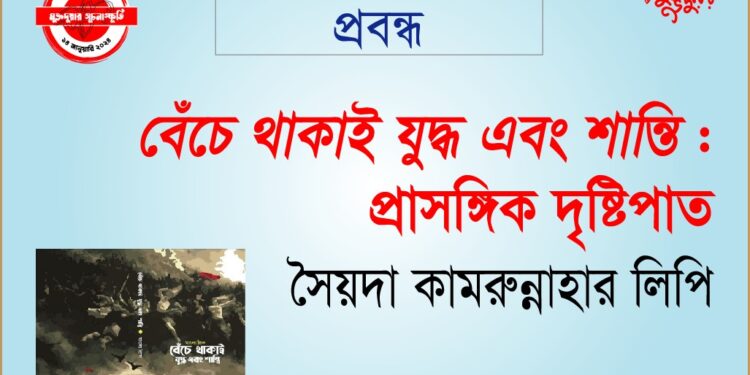
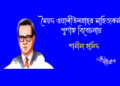








Discussion about this post