ইফফাত আরা ইভা
মাওলা প্রিন্সের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি (২০২২)। করোনাকালীন অবরুদ্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে এক বা একাধিক বিস্মিত শ্রোতার কাছে উপন্যাস-কথক তার জীবনেতিহাস বলে যাচ্ছেন। পুরো উপন্যাসে কথা বলে কেন্দ্রীয় চরিত্র কথক। কথকের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে যাওয়া দিনগুলোর আখ্যান জীবন্ত হয়ে উঠে উপন্যাসের সুবিস্তৃত পরিসরে। উপন্যাসটি শুরু হয় করোনাভাইরাসজনিত মৃত্যুচেতনার উৎকণ্ঠা ও বিষণ্নতার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় কথক ও তার প্রিয়তমা স্ত্রীর করোনার উপসর্গ নিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চরম আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরমধ্যে স্থান পায় ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক জীবনপ্রবাহের নানা চালচিত্র। প্রতিটি মানুষের বেড়ে ওঠার পেছনে তার পরিবেশ ও প্রতিবেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। তেমনি একজন লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করার মতন প্রচুর উপকরণ তাঁর প্রতিবেশে ছড়িয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্সের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি তাঁর বোধ ও মননের ক্ষেত্রভূমিতে পরিবেশ ও প্রতিবেশজাত উপকরণগুলো তুলে এনে উপন্যাস-শিল্পে স্থান দিয়েছেন। আখ্যান কিংবা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট স্থানিক পটভূমির সাক্ষাৎ মেলে। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে যে কয়টি স্থানিক পটভূমির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল। ঔপন্যাসিকের শৈশব-কৈশোরের বেড়ে ওঠার দিনগুলো যেখানে অতিবাহিত হয়েছে। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের কথক তার অভিজ্ঞতার শানিত ভাষায় মানুষের জীবন ও আর্থসামাজিক অবস্থাকে খুব কাছে থেকে প্রকাশের তাগিদে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পটভূমি বেছে নিয়েছেন। কাহিনি ও চরিত্রের প্রয়োজনে কিংবা লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রভাবের কারণে উপন্যাসে স্থানিক পটভূমির নিবিড়তা পাঠকের মনঃসংযোগকে সেই বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে একাত্মতা প্রদান করে।
বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের আখ্যানবিস্তারে মৃত্যুচিন্তা অনিবার্য অনুষঙ্গরূপে প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্যুর পর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজরিত ছায়া-সুনিবিড় গ্রামে কবর রচনার আশা পোষণ করেন উপন্যাস-কথক। এই সূত্রে প্রকৃতির মাঝে টিকে থাকা উত্তরবঙ্গের এক শান্ত সুনিবিড় গ্রামের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটে। যে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবেশে কথকের প্রথম স্বপ্ন-কল্পনার বীজ রোপিত হয়েছিল। কথকের জন্মভূমি তথা তার স্ব-গ্রামের পরিচয় প্রদানে ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক সিদ্ধির প্রকাশ ঘটে :
মৃত্যু হলে কবরটা কোথায় হবে, অবশ্যই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় চির চেনা জন্মভূমিতে, শহরের নয় গ্রামের বাড়িতে, নাড়িছেঁড়া ও নাঁড়িপোতা মাতৃকামূলে, মাতৃকাজঠরে। ওখান থেকেই যে বেড়ে ওঠা, শৈশব-কৈশোরের স্বপ্ন-কল্পনা এবং জীবনকে প্রথম অনুভব করা; সেই কালো দোআঁশ মাটির সোঁদাগন্ধ, সাদা ভাটফুলের তীব্র ঘ্রাণ, সবুজ বাতাবিলেবুর মিষ্টি সুবাস, হলদে শঠি আর আদা ক্ষেতের অদ্ভুত বাস্না, ক্ষুদে মৌরি ফুলের সুরভি, মস্ত-মস্ত পাকা কাঁঠালের মৌ-মৌ খুশবু শরীর-মন-মস্তিষ্কে একদিন যে রাঙা পরাগরেণু মাখিয়ে দিয়েছে, দিয়েছিলো, তা-ই তো আমার ঔজ্জ্বল্য, তা নিয়েই তো চলছি, বেঁচে আছি। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৪২)
মানবজীবন ও সমাজের অস্তিত্বের জন্য, এর বিকাশের প্রয়োজনে প্রকৃতি একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। প্রকৃতির যে পরিবেশে মানবসমাজ টিকে থাকে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে জীবিকা ও সমাজব্যবস্থার একটি প্রত্যক্ষ-সংযোগ তৈরি হয়, সেটাকে বলা হয় ভৌগোলিক পরিবেশ। ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হলে সে অঞ্চলের উৎপাদন প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়ে এর সামূহিক বিকাশ দ্রুত হয়। অন্যদিকে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে উৎপাদনের বিকাশ শ্লথ হয়ে থাকে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে মানুষের জীবন ও অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ে। তাদের জীবনপ্রণালি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পলে পলে। মানুষের জীবনযাপনের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের দূরপ্রসারী প্রভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্র নিরূপণে বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাস ঔপন্যাসিকের একনিষ্ঠ শৈল্পিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। জীবনপ্রকাশের অনিবার্য সূত্র ধরে এ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চল, আর এই উঁচু অঞ্চলের পানি দ্রুত নিম্নাঞ্চলে গড়িয়ে পড়ার কারণে খুব দ্রুতই এখানে খরার সৃষ্টি হয়। এসমস্তকিছুই ঔপন্যাসিকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে উপন্যাসের আখ্যানভাগের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ভূ-প্রকৃতির জন্য এখানকার নদী ও পুকুরগুলো দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ এ অঞ্চলের বাসিন্দারা পেত না। এছাড়া চাষের জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থাও ছিল না। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জমিতে পানি দেয়ার প্রসঙ্গের অবতারণা করে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন :
[…] মরাসতী নদীতেও প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো, মেজো আঙ্কেল রাত জেগে হ্যাচাক না-কি হ্যাজাক লাইট হাতে খোঁচা দিয়ে মাছ মারতেন, পলো দিয়ে মাছ ধরতেন; কিন্তু, ওটা সারা বছরের চিত্র নয়, হয়তো বছরের কোনো এক ক্ষুদ্র সময় এ্যামোন বড় বড় মাছ আসতো, ধরা পড়তো, যাই হোক, প্রায় সারা বছর উত্তরবঙ্গের মানুষ খরার সঙ্গে যুদ্ধ করতো, তখন ডিপকল কিংবা স্যালো মেশিন ছিলো না বললেই চলে, বিদ্যুৎ তো সব জায়গায় ছিলো না, ডিপকল আসবে কোথা থেকে, আমাদের পায়ে চালানো পানির কল ছিলো, একজন মানুষ দুটো বাঁশে পা রেখে হাঁটবার মতো করে চাপ দিলে জোড়া কল থেকে পানি বেরুতো, সেই পা-কলও এসেছে অনেক পরে, আমার জ্ঞান হওয়ার পরে, সম্ভবত আরডিআরএস তা নিয়ে এসেছে, এনেছিলো, পরিচিত করেছে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৭)
উপন্যাস-কথকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মাধ্যমে এভাবেই জীবন্ত হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের নিরন্তর হাড়ভাঙা পরিশ্রম, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি মাটি কামড়ে পড়ে থাকার জীবনযুদ্ধ। কথকের পরিবারের দারিদ্র্যের চিত্র উন্মোচন সূত্রে ঔপন্যাসিক পৌঁছে যান জাতীয় অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও প্রশাসননীতিতে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার ইতিহাসের গভীরে। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে যেখানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের শতকরা হার ক্রমশ নিম্নমুখী, উত্তরবঙ্গ সেখানে ব্যতিক্রম। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বিরূপ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এ অঞ্চলটির দিকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন থাকলেও বাস্তবে তা আলোর মুখ দেখেনি। এ অঞ্চলের সংগ্রামমুখর মানবগোষ্ঠীর অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দুর্বল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্যের চিত্র উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্স বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন :
রংপুর বিভাগে ২০১৬ সালেও দারিদ্র্যের হার ছিলো বা হচ্ছে ৪৭.২% এবং দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপ্রবণ দশটি জেলার পাঁচটিই রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলা; অবশ্য ২০১০ সালে রংপুর অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ছিলো ৪২.৩%; তাহলে, কী দাঁড়ালো, নিশ্চয়ই সরকার এই অঞ্চলের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয় নি, কিংবা, কোনো কার্যকরী উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা, বঞ্চনা করেছে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলকে, পুরো উত্তরবঙ্গকে! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৯)
বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি কেবল পটভূমি হিসেবেই নয়, পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতীক হিসেবে সমধিক গুরুত্ববহ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রদবদলে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোয় বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন এলেও এ অঞ্চলের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী কার্যকর কোনো পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়নি। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের শিক্ষিত ও সচেতন মহলের প্রাণের দাবি এ উপন্যাসে শিল্পিত অবয়ব পায় ফ্ল্যাশব্যাকে :
অথচ, পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী এই অঞ্চলটির সমৃদ্ধি সাধনে করার মতো অনেক কিছুই ছিল। রংপুর অঞ্চলের শিক্ষিত, সচেতন ও সুধীমহলের আজ প্রাণের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে, উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর, বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের আটটি জেলার সমন্বয়ে রংপুরকে বিভাগ ঘোষণা, রংপুরে একটি পৃথক শিক্ষাবোর্ড গঠন, যার প্রয়োজনীয়তার কথা কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৮১)
বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে প্রকৃতি-বর্ণনা কেবল নিসর্গচিত্রণ নয়, তার মাঝে আরও সুগভীর বক্তব্য লুকিয়ে থাকে বিশাল ব্যপ্তি নিয়ে। এ উপন্যাসে কথক তার পরিবারের জীবন কাহিনি বর্ণনা করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের গ্রামের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনার দিকে অভিনিবেশ স্থাপন করেছেন। যেখানে মূলত উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠে :
আমরা তখনো গ্রামের বাড়িতে থাকতাম; দক্ষিণদিকে মেজো ও সেজো আঙ্কেলের বাইশ বা চব্বিশ হাতি চকচকে টিনের ঘর, ঘরের পিছনে এক সারি সুপারি গাছ, ফাঁকে ফাঁকে নিম আর সুকাতি, পাশে একটা দারুচিনি গাছের সঙ্গে একটি ডালিম গাছ ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে নববধূর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে; […] রাস্তার পাশে জাম গাছের বিপরীতে একটি কাঁঠাল গাছের তলে দেখবে বাঁশের তৈরি একটি প্রশস্ত টং বা বসবার মাচা, তুমিও সেখানে বসতে পারো, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারো, সামনের পুকুরের স্বচ্ছ পানি দেখতে দেখতে মধুর কোনো গল্প করতে পারো গ্রামের দু-চার-পাঁচটা মানুষের সঙ্গে ওখানেই, ওরা তোমাকে সঙ্গ দেবে, ওরা তোমাকে ওদের আনন্দ, বেদনা, হতাশার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ শোনাবে; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৩-৭৪)
ব্যক্তির বাহ্যিক ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণে বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসটি বিশিষ্ট হলেও এখানে একটি অঞ্চলের সামষ্টিক মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভূ-প্রকৃতিগত বিশিষ্টতাই তাদের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পেছনে নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের সহজ-সরল-অতিথিপরায়ণ জনমানুষের চিত্রায়ণ যৌথ ব্যঞ্জনা পায় এখানে। কারণ, ভূ-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে একটি অঞ্চলের মানুষের চরিত্র, তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনাচারকে। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক উত্তরবঙ্গের মানুষের দারিদ্র্যের তত্ত্বীয় বা তাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি তাদের চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করেছেন; যা তাদের দারিদ্র্যের পেছনে পরোক্ষ প্রণোদনা যুগিয়েছে। এরকম কিছু শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের উল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যায় : “সহজ, সরল, সৎ, আদর্শিক, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, আবেগপ্রবণ, বোকা, হাবা, হাবাগোবা, অলস, আলসিয়া, কুড়ে, কুড়িয়া, অনুভূতিহীন, পাষাণ, উদাসীন, বাউদিয়া, কামচোরা, রসিক, মফিজ ইত্যাদি।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৮৩) এভাবে উৎপাদনপ্রক্রিয়া শ্রেণিভুক্ত মানুষের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে, যে উৎপাদন-প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয় একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর দ্বারা। আবার, এই জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতিই তৈরি করে সেই অঞ্চলের জনমানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের রূপ কেবল জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির মধ্যে খুঁজলে সবসময় পাওয়া যায় না; স্থানীয় জনজীবন, পরিবেশ, আর্থসামাজিক অবস্থা, সংস্কার— সবকিছুর সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করা উচিৎ। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ও মার্চ থেকে এপ্রিল— এই পাঁচ মাসে কৃষিকাজ না থাকায় রংপুরের পাঁচ জেলার লোকজন বেকার হয়ে পড়ে। মৌসুমী এই বেকারত্বের কারণেই দেখা দিত খাদ্যের অভাব। এটাই উত্তরবঙ্গের ‘মঙ্গা’ নামে পরিচিত। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে উপন্যাস-কথকের স্মৃতিতে মঙ্গাকালীন ক্ষুধা-দারিদ্র্যের পাশাপাশি সামাজিক সঙ্কট ও সমস্যা শৈল্পিক অভিব্যক্তি পায়। মানুষের আয়-উপার্জন যখন বন্ধ হয়ে যায়, হাতে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা না থাকলে, ঘরে খাবার না থাকলে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ-কলহের প্রবণতা বেড়ে যায়। এরকমই একটি দাম্পত্য কলহের চিত্র ঔপন্যাসিকের সরস রসিকতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে :
নিশ্চয় জানো যে, হাতে টাকা-পয়সা না থাকলে, উৎপাদন-উপার্জন বন্ধ হলে, কিংবা ঘরে খাবার না থাকলে মানুষের রাগ-ক্ষোভ-ঝগড়া বেড়ে যায়, জীবনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা আসে। হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? আমাদের গ্রামের বাড়ির বাঁশঝাড়ের পেছনে যে ছোট ছোট বাড়িগুলো গাদাগাদি করে ছিলো, আছে, থাকে, একদিন ওখানকার একজন তার বউকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিলো; কিন্তু, সংস্কার ও রূঢ়বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বউটি বাপের বাড়ি ফেরত যেতে চাচ্ছিলো না; লোকটি তার বউকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় বা পুকুরপাড়ে এনেছে; তখন, তাদের বাকযুদ্ধ হচ্ছিলো, চলছিলো; ক্রোধী লোকটি বলে, বলছিলো, সাউয়্যাডাংরি মাগি, মোর বাড়ি থাকি ব্যারাও। তখন মুখচুত্তি বা ঝালমুখী মহিলাটি বলে, বলছিলো, বাল্ কামার ব্যাটা, হোলোত্ জোর নাই, আর মোকে কইস্ সাউয়্যাডাংরি, ভাত দিব্যার পাইস্ না, আর কইস্ ভাতার! তখন, লোকটি আরো উত্তেজিত হয়ে বলে, বলছিলো, বলেছিলো, মাগি, তোর সাউয়্যাত্ বাসনা নাই, তোর সাউয়্যা বাসায় না, গোন্দায়, ভকভক করি গোন্দায়, ওয়াক থু! ছোটখাটো কিংবা দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটিও দমে যাওয়ার পাত্রী নয়, বলে, জারুয়্যার ব্যাটা জারুয়া, মোর সাউয়্যা এ্যাতোদিন বাসাইছিলো, এ্যালা গোন্দায়, এ্যালা যে কামাই নাই, এইজইন্যে গোন্দায়! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৮৩-৮৪)
উত্তরবঙ্গের মানুষের আর্থসামাজিক জীবনাচার ও এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়াও বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের ঘটনাংশের বিস্তারে এখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন বর্ণিল হয়ে উঠেছে। নতুন ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষ নবান্নের উৎসবে মেতে ওঠে। নবান্ন উৎসব তাদের জীবনে বিনোদনের অপার উৎস। কাকলী অপেরা পার্টি যাত্রা গান, দি নিউ সোনার বাংলা সার্কাস, বাংটু জাদুকরের বিখ্যাত জাদুখেলা, পুতুল নাচ, বুলবুল সার্কাস, শ্যামলী অপেরার উল্লেখে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে বাঙালির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয় পাঠকের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। উপন্যাসে আরও পাওয়া যায় :
[…] হয়তো খচরের দিঘিতে শুরু হবে ঘুড়ি উড়ানো উৎসব, কিংবা, ঘুড়ি কাটাকাটি প্রতিযোগিতা, হয়তো সাপ্টিবাড়ি বাজারে শুরু হবে হাঁটিবাড়ি কিংবা ডাকার মেলা, হয়তো যত্রতত্র শুরু হবে টেক-টেক-টেক অর্থাৎ হাডুডু প্রতিযোগিতা, বিস্তৃত ও পরিচ্ছন্ন মাঠের অভাবে ফুটবল খেলা তখন বিশেষভাবে জমে উঠে নি, কিন্তু, ফসল তোলার পর পরিত্যাক্ত মাঠে ফুটবল খেলা হতো; ফিতা কিংবা জুয়া কিংবা চান-ফুল পয়সা খেলার আসর জমতো বা জমবে আগানে-বাগানে, রাস্তার উপরেই; (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৭৮)
উত্তরবঙ্গের বিশাল এক জনগোষ্ঠী তিস্তার পানিপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিকের বাস্তবসচেতন প্রাজ্ঞদৃষ্টি এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়নি। উত্তরবঙ্গের জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে তিস্তা নদী এবং এর বিভিন্ন শাখানদী সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য-উপাত্ত স্থান পেয়েছে বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে। তিস্তা নদী ভারত ও বাংলাদেশের একটি অভিন্ন নদী। বিশ্বব্যাপী অভিন্ন নদীগুলোর পানি ভাগাভাগিতে পানির অভাব ও অভাবপ্রসূত সংকটকে সম্মিলিতভাবেই মোকাবিলা করা হয়। কিন্তু, নিজ স্বার্থে তিস্তার পানি নিয়ে ভারতের একতরফা কার্যক্রম বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নির্মোহ নিরাসক্তি নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে পরাবাস্তবতার আশ্রয়ে, শিল্পিতভাবে :
ওসব তো কৃত্রিম বন্যা, ইন্ডিয়ার তৈরি, অন্যসময় পানি থাকে না, আর, বর্ষাকালে ওদের বাঁধগুলো একসঙ্গে খুলে দিয়ে আমাদের মারে, বাংলাদেশের মরণ দেখে। তখন একটা আর্তনাদ কিংবা হাহাকার উঁকি দেয়। তখন আর্তনাদ ও হাহাকার অসংখ্য চামচিকে হয়ে আকাশ ভরিয়ে তোলে। তখন দুপুরকেও রাত বলে ভ্রম হয়। রাতের আকাশকে ভয়ঙ্কর কোনো দৈত্যের মতো দেখায়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উড়ন্ত চামচিকার ভীষণ চিৎকারে চিৎকারে পৃথিবীর কর্ণবিবর মুহূর্তেই বিকল হয়ে পড়ে। কর্ণপট থেকে ফিনকি দেয়া রক্তের ছিটে বুকের উপরের পোশাকে লাগে। একটুখানি রক্তের ছিটে একটু একটু করে জামা, টি-শার্ট, গেঞ্জি, সেমিজ, ব্রা, পেন্টি, জাঙ্গিয়া ভিজিয়ে দেয়। মনোযোগ অন্যত্র থাকায় প্রথমে ব্যাপারটা ওরা বুঝে উঠে না। ওরা মনে করে যে ওরা ঘামছে। ভ্যাপসা গরমে ওরা ঘর্মাক্ত, ঘেমে যাচ্ছে। খুব গরম পড়ায় ওদের শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ছুটছে, পড়ছে। একপর্যায়ে ওরা জামা, টি-শার্ট, গেঞ্জি, সেমিজ কিংবা ব্রার ভেতর নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘাম ভেবে রক্ত মুছে ফেলে। এভাবে নখের কোণে আর হাতের তালুতে লেগে থাকা রক্ত নাক, মুখ, কপাল, ভ্রূ, চিবুক, কিংবা, পিঠ চুলকানোর সময় ছড়িয়ে যায়। একসময় ওদের ফর্সা কিংবা দুধেপাটালি দেহ আর জামা-কাপড় রক্তে লেপ্টালেপ্টি হয়, জবুথবু হয়ে পড়ে। তখন ওরা চমকে উঠে! তখন তারা দিশেহারা হয়। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৯৯-২০০)
মঙ্গাপীড়িত এক অঞ্চল থেকে এ উপন্যাসের কথকের সত্যের পথে অবিরাম যাত্রা। এই যাত্রায় নিজের অবস্থানবিন্দু সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে সে, যা তাকে জ্ঞান ও আলোর পথ দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ অংশটিতে ঔপন্যাসিক বৈশ্বিক চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। উপন্যাস-কথকের বর্ণনায় পাওয়া যায় :
পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, একবার ভাবো তো; পৃথিবীর অনুন্নত কিংবা গরিব মহাদেশ হলো এশিয়া, এশিয়ার অনুন্নত কিংবা গরিব অঞ্চল হলো দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার অনুন্নত কিংবা গরিব দেশ হলো বাংলাদেশ, বাংলাদেশের অনুন্নত কিংবা গরিব অঞ্চল হলো উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের অনুন্নত কিংবা গরিব অংশ হলো আমাদের জেলা, আমাদের জেলার একটি অনুন্নত কিংবা গরিব গ্রাম হচ্ছে নায়েকগড়হারাটি, সেই নায়েকগড়হারাটি গ্রামের একটি অনুন্নত কিংবা অতি সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা; তাহলে বৈশ্বিক মানচিত্র ও বিশ্বপরিক্রমায় আমার অবস্থানবিন্দু কোথায়? (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৪৬)
নির্দিষ্ট শব্দবন্ধের সমন্বয়ে পাঠক ও লেখকের জীবনবোধ আদান-প্রদানের একটি প্রতীক-মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। এই মাধ্যমটিকে কেন্দ্র করে লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎ শানিত হয়। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের গদ্যভাষা নির্মাণে ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্স নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সে নিরীক্ষায় তাঁর দীর্ঘ শ্রম ও সময় ব্যয়ের দৃষ্টান্ত সহজেই অনুধাবনযোগ্য। বিষয়ের মেজাজ অনুযায়ী বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের ভাষার শিল্পসৌধ নির্মিত হয়েছে। অলোচ্য উপন্যাসের ভাষারীতিতে একইসঙ্গে প্রমিত ও আঞ্চলিক রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার প্রয়োজনে এখানে আঞ্চলিক রীতিতে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ভাষার অবাধ প্রয়োগ লক্ষযোগ্য। এক্ষেত্রে করোনাকালীন মৃত্যুযাত্রার চিত্রকল্পে ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের রংপুরী উপভাষার অনন্য উদাহরণ :
হামরা যারা পাবার নই বাহে, হামার ম্যালা কাম বাকি আছে বাপু, হামার ঘুম আছে, হামরা আর এ্যাকনা ঘুমামো, নিন্ যামো, তারপরোত্ সুমায় হইলে আসমো, তুমরা যাও, তুমরা যাও, তুমরা চলি যাও বাহে, আর আইসেন না বায়ো, হামার যাবার শখ নাই, ইচ্ছা নাই, আল্লাদ নাই, শক্তিও নাই বাপু…, ফির ডাকেন ক্যা বাহে, অতো জোরে জোরে ডাকেন ক্যা, অতো অতো হাকেন ক্যা, হামার ঘুম নষ্ট করেন ক্যা, আসমান কি কালা কুটকুটা হইছে, ধুমা দিয়্যা ঢাকি গেইছে দেওয়্যা, দজ্জাল কি আইসছে, জানোয়ার দব্বাহ কি ব্যারাইছে, পশ্চিম দিকোত্ কি সূয্য উইঠছে, ঈসা নবি কি ফির আইসছে, পূব আর পশ্চিম দিকোত্ কি মাটি ঘটোর-ঘটোর করি কাঁইপপ্যার নাইগছে, ইয়েমেনোত কি আগুন ভলভল করি জ্বইলব্যার নাইগছে; হামাক ক্ষমা করো বাহে, হামরা তুমার সাতে যাবার নই, হামরা তুমার পাছোত্ তুমার সাতোত্ যাবার নই…। (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ৪৯)
অনুরূপ, কথকের মায়ের মুখে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রকাশ লক্ষণীয় :
তখন কিংবা অন্য এক সময়ে মা বলবে, বলবেন, আমাদের জীবনটা হইলো কুত্তা-বিড়ালের জীবন, টানি-টানি ছেঁচড়ি-ছেঁচড়ি চলা জীবন, প্যাটোত পাথর বান্দি ত্যানা-কাপড় পরি ধাকরি-ধুকরি কোনোমতে বাঁচি থাকার জীবন; বাপের সংসারে শান্তি পাই নাই, ভাত থাকিয়াও ভাতের কষ্ট পাইছি, স্বামীর বাড়িত্ আসিয়্যাও কষ্ট; এ্যাটে খালি ভাতের কষ্ট নয়, ভাতের সাতে কাপড়েরো কষ্ট! (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১১১)
করোনাকালীন অবরুদ্ধ সময়ের সামূহিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত হওয়ায় এর ভাষায়ও সংশয়বোধের সংশ্লেষ ঘটেছে। অসংখ্য ‘কিংবা’র সমন্বয়ে উপন্যাসের বাক্যগুলো যেন বিকল্প এক প্রতিবিশ্ব নির্মাণে বদ্ধপরিকর। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বজুড়ে সময়ের ফ্রেম ভেঙে দিয়েছিল। মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত মানুষের জীবনে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কাঠামো বিপর্যস্ত। বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসের ভাষা সেই ভঙ্গুর সময়ের রূপায়ণে একনিষ্ঠতার সাক্ষর রেখেছে। একই বাক্যে অতীত থেকে বর্তমান কিংবা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে অবাধ যাতায়াতের এমন দৃষ্টান্ত বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। উপন্যাস-কথক “সময়ের চক্রাকারে বুঝে উঠতে পারে না কিংবা পারেন না আজ কয় তারিখ, এটা কি মাস চলছে, এটা দুই হাজার উনিশ না-কি দুই হাজার বিশ সাল? তখন সে বা তিনি হয়তো দেয়ালে ঝুলানো ক্যালেন্ডারে চোখ বিদ্ধ করবে, চক্ষু স্থির করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন; কিন্তু, বুঝতে পারবেন না এটা জুলাই না আগস্ট মাস, অথবা, জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর তিন মাসের একটি পাতা দেখে সে তখন অসন্তুষ্ট হবে।” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৭৯-১৮০) বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ, বাক্য গভীর অর্থদ্যোতকতা বহন করে। ভাষার সংহত কাঠামোয় বিস্তৃত অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে উপন্যাসের ভাষা সাংকেতিক বা প্রতীকময় হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন ব্যক্তি ও সমষ্টির সামূহিক বিনষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকার মন্ত্র উন্মোচন সূত্রে মানবমুখী ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্স এ উপন্যাসে প্রতীককে ব্যবহার করেন জোরালোভাবে। প্রতীকের সার্বভৌম শক্তি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্মায়িক রূপ। করোনা ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করলে সর্বত্র হতাশা, বিষাদগ্রস্ততা, অবসন্নতা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে। একটুকু শান্তি কিংবা স্বস্তির আশায় পৃথিবীবাসী যখন তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষমান, তখন বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে কবুতরের প্রতীকে ঔপন্যাসিক শান্তির বার্তা পৌঁছে দেন। উপন্যাসে কবুতর বা পায়রার প্রসঙ্গটি এভাবে ব্যক্ত : “কবুতর শান্তির প্রতীক […] ভুয়ো কোভিড করোনা টেস্ট ও ভুয়ো টেস্ট বাণিজ্যের নষ্টকথা বাদ দিয়ে এসো আমরা কিছুক্ষণের জন্য আশাজাগানিয়া পায়রার বাকবাকুম বাকবাকুম কুম-কুম-বাক শুনি!” (মাওলা প্রিন্স, ২০২২ : ১৭৬) পায়রা ছাড়াও এ উপন্যাসে সাপ, কাক, বানর, শূকর ইত্যাদির প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। চারিদিকে শত্রু পরিকীর্ণ অবক্ষয়িত সমাজে সাপের প্রতীকে শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন লেখক। জীবনের দৃশ্যমান-অদৃশ্য অসঙ্গতি ও শত্রু-কবলিত বন্দীদশা রূপায়ণে ঔপন্যাসিক সাপের প্রতীক ব্যবহার করেছেন অনিবার্য প্রকরণ হিসেবে।
মাওলা প্রিন্সের বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসে একচ্ছত্রভাবে না হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কথকের শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণার উন্মোচন সূত্রে উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আঞ্চলিক উপাদানবলির প্রয়োগ ঘটেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র কথকের স্মৃতিতে উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো বহির্সত্য ও অন্তর্সত্যসমেত এখানে ধরা দেয়। এই অঞ্চলের হতভাগ্য মানবগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা, সামাজিক সংকট ও সম্ভাবনার কথা চিত্রিত হয়েছে সীমাহীন মমত্বে। ঔপন্যাসিক মাওলা প্রিন্স এখানে অবিরাম বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন সংসার ও সমাজের প্রতি; সংস্কৃতি ও বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে জাতির প্রতি। তারপরও এ উপন্যাসে পরিবার, সমাজ, সংসার, ধর্ম, আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে করোনাকালীন অবরুদ্ধ বৈশ্বিক পরিবেশে ব্যক্তির অন্তর্দহন ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বস্তুত, ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার নিজস্ব পাদপীঠ থেকে বেঁচে থাকাই যুদ্ধ এবং শান্তি উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ঊষর উত্তরবঙ্গের প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতির যেরূপ চিত্রায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে, সেখানে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানবগোষ্ঠীর নিরন্তর সংগ্রাম কেবল বাংলার এই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বৈরী প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনগাঁথা হয়ে ওঠে। সবটাই উপন্যাস-কথকের স্মৃতিময় চেতনাসমৃদ্ধ বোধের ফসল।

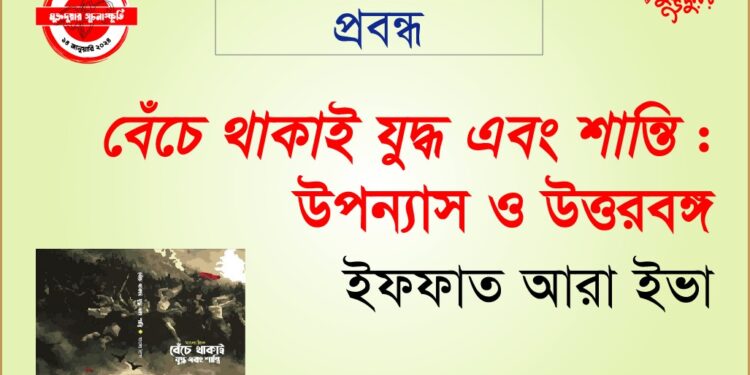
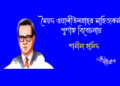





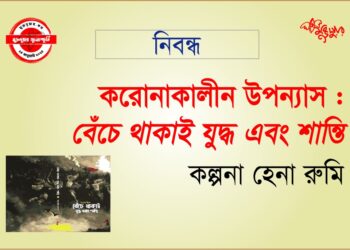


Discussion about this post